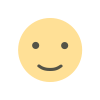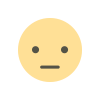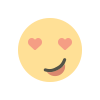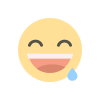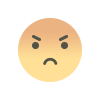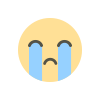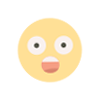এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। যশোর বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। যশোর বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
১. (ক) উদাহরণসহ ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম:
ম-ফলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে যা শব্দের সঠিক উচ্চারণ নির্ধারণ করে। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. শব্দের আদিতে ম-ফলা: শব্দের শুরুতে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ সাধারণত অনুচ্চারিত থাকে এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য হয়।
* উদাহরণ: স্মরণ (উচ্চারণ: শোরোন), স্মৃতি (উচ্চারণ: শ্রি-তি)।
২. শব্দের মাঝে বা শেষে ম-ফলা: শব্দের মাঝখানে বা শেষে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ প্রায়শই বজায় থাকে এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে।
* উদাহরণ: পদ্ম (উচ্চারণ: পোদ্-দো), আত্মা (উচ্চারণ: আত্-তা)।
৩. গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল, শ, ষ, স - এই বর্ণগুলোর সাথে ম-ফলা: এই বর্ণগুলোর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-এর উচ্চারণ সাধারণত অনুচ্চারিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বর্ণের উচ্চারণ নাসিক্য হয়।
* উদাহরণ: বাগ্মী (উচ্চারণ: বাগ্-মি), যুগ্ম (উচ্চারণ: জুগ-মো)।
৪. যুক্তব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা: যদি কোনো যুক্তব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা যুক্ত হয়, তবে ম-এর উচ্চারণ প্রায়শই অনুচ্চারিত থাকে এবং যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের ওপর জোর পড়ে।
* উদাহরণ: লক্ষ্মণ (উচ্চারণ: লক-খোঁন), ভস্ম (উচ্চারণ: ভশ-মো)।
৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে: অনেক সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে ম-ফলা তার নিজস্ব উচ্চারণ বজায় রাখে, বিশেষ করে যখন এটি একটি শব্দের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
* উদাহরণ: শ্মশান (উচ্চারণ: শ্মো-শান), ব্রহ্মা (উচ্চারণ: ব্রোম-হা)।
১. (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ:
-
অধ্যক্ষ: ওদ্ধোক্খো
-
আবৃত্তি: আব্রিত্তি
-
অদ্বিতীয়: ওদদিত্তিয়
-
ঐকতান: ওইকোতান্
-
সহস্র: শোহোশ্রো
-
স্মরণীয়: শোরোনিও
-
জ্ঞাপন: গ্অ্যাপোন
-
স্মর্তব্য: শ্মোর্তোব্বো
২. (ক) বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম:
বাংলা বানানে মূর্ধন্য 'ণ' (ণত্ব বিধান) ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, বিশেষ করে তৎসম (সংস্কৃত থেকে আগত) শব্দের ক্ষেত্রে। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম দেওয়া হলো:
১. ঋ, র, ষ এর পর ণ: ঋ, র, এবং ষ এই তিনটি বর্ণের পর সবসময় মূর্ধন্য 'ণ' হয়, যদি মাঝখানে অন্য কোনো স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গীয় বর্ণ (প, ফ, ব, ভ, ম), য, য়, হ, অথবা অনুস্বার (ং) না থাকে।
* উদাহরণ: ঋণ, কারণ, তৃণ, বর্ণ, কর্ণ, মরণ, ভীষণ, ভূষণ, বিষণ্ণ।
২. ট-বর্গীয় বর্ণের সাথে ণ: ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ) বর্ণের সঙ্গে যুক্তাক্ষর হিসেবে সবসময় মূর্ধন্য 'ণ' হয়।
* উদাহরণ: কণ্টক, লুণ্ঠন, দণ্ড, খণ্ড।
৩. প্র, পরা, পূর্ব, অপর, নির - এই উপসর্গগুলোর পর: কিছু তৎসম উপসর্গ, যেমন 'প্র', 'পরা', 'পূর্ব', 'অপর', 'নির' ইত্যাদির পর গঠিত শব্দে 'ণ' হয়।
* উদাহরণ: প্রণাম, প্রাণ, পরিনাম, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, নির্ণয়।
৪. কিছু নির্দিষ্ট তৎসম শব্দে স্বাভাবিভাবে 'ণ': কিছু তৎসম শব্দে 'ণ' এর ব্যবহার সহজাত বা স্বাভাবিক, যা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না। এদেরকে স্বভাবতই ণ-ত্ব বিধান বলা হয়।
* উদাহরণ: চাণক্য, মাণিক্য, গণনা, বাণিজ্য, লবণ, বেনু, বীণা, কল্যাণ, বাণিজ্যিক।
৫. ন-এর ণ-তে পরিবর্তন: কিছু ক্ষেত্রে, র-এর পরে অবস্থিত 'ন' মূর্ধন্য 'ণ'-এ রূপান্তরিত হয়, বিশেষ করে সমাসবদ্ধ পদ বা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শব্দে।
* উদাহরণ: অগ্রনায়ক (অগ্র+নায়ক থেকে), সর্বাঙ্গীণ (সর্বাঙ্গ+ইন)।
২. (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
-
আবিষ্কার (আবিস্কার)
-
প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দিতা)
-
শহিদ মিনার (শহীদমিনার) - এটি দুটি আলাদা শব্দ।
-
উচ্ছৃঙ্খল (উশৃঙ্খল)
-
নূন্যতম (ন্যূনতম)
-
নিশুতি (নিশিথিনী - 'নিশিথিনী' বলতে গভীর রাত্রি বোঝায়, যা 'নিশুতি'র কাছাকাছি; তবে 'নিশুতি' অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। যদি 'নিশিথিনী' সঠিক বানান হয়, তবে এটি নিজেই শুদ্ধ। কিন্তু প্রশ্নে সম্ভবত 'নিশিথ' থেকে আসা কোনো ভুল বানানকে বোঝানো হয়েছে। প্রচলিত ভুল বানান 'নিশিথিনী' হলে শুদ্ধ রূপ 'নিশুতি' বা 'নিশীথ')। তবে এখানে 'নিশীথিনী' হলে সেটি ভুল নয়। ধরে নিচ্ছি প্রচলিত ভুল বানান 'নিশিথিনী' এর পরিবর্তে 'নিশীথিনী' শুদ্ধ।
-
মুমূর্ষু (মুমুর্ষু)
-
সায়াহ্ন (সায়াহ্ণ)
৩. (ক) ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা:
ক্রিয়াপদ হলো সেই পদ যা দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া বা ঘটা বোঝায়। প্রতিটি বাক্যের অপরিহার্য অংশ হলো ক্রিয়াপদ, কারণ এটি ছাড়া বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।
উদাহরণ:
-
ছেলেটি খেলছে। (এখানে 'খেলছে' কাজটি নির্দেশ করছে।)
-
ফুলটি সুন্দর। (এখানে 'সুন্দর' দ্বারা অবস্থা বোঝাচ্ছে, যদিও এটি একটি নাম বিশেষণ, এর ক্রিয়াপদ 'হয়' উহ্য আছে।)
-
সূর্য উঠছে। (এখানে 'উঠছে' একটি ঘটনা নির্দেশ করছে।)
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে সাধারণত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে প্রধান কিছু শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং বাক্যটি শেষ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: সে ভাত খায়। (এখানে 'খায়' ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে।)
২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না এবং বাক্যটি আরও কিছু অংশের উপর নির্ভর করে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে 'ইয়ে', 'লে', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত থাকে।
* উদাহরণ: সে খেয়ে ঘুমালো। (এখানে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া, যা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করেনি।)
৩. সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, অর্থাৎ যাকে প্রশ্ন করলে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: বাবা বই পড়েন। (এখানে 'কী পড়েন?' - 'বই', তাই 'পড়েন' সকর্মক ক্রিয়া।)
৪. অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, অর্থাৎ যাকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: ছেলেটি দৌড়ায়। (এখানে 'কী দৌড়ায়?' বা 'কাকে দৌড়ায়?' - কোনো উত্তর নেই, তাই 'দৌড়ায়' অকর্মক ক্রিয়া।)
৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে (একটি মুখ্য কর্ম এবং একটি গৌণ কর্ম), তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়।
* উদাহরণ: শিক্ষক ছাত্রকে বাংলা শেখাচ্ছেন। (এখানে 'ছাত্রকে' গৌণ কর্ম এবং 'বাংলা' মুখ্য কর্ম।)
৬. যৌগিক ক্রিয়া: দুটি ক্রিয়াপদ একত্রিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে এটি গঠিত হয়।
* উদাহরণ: মেয়েটি খেতে বসল। (এখানে 'খেতে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'বসল' সমাপিকা ক্রিয়া মিলে যৌগিক ক্রিয়া।)
৭. প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজটি করায়, তখন তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যে কাজ করায় সে প্রযোজক কর্তা এবং যাকে দিয়ে কাজ করানো হয় সে প্রযোজ্য কর্তা।
* উদাহরণ: মা শিশুকে গল্প শোনাচ্ছেন। (এখানে মা প্রযোজক কর্তা, শিশু প্রযোজ্য কর্তা এবং 'শোনাচ্ছেন' প্রযোজক ক্রিয়া।)
৩. (খ) নিম্নরেখ যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ:
ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে বাক্যের মধ্যে পদের কার্যকারিতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যাস করাকে বোঝায়। নিচে নির্দেশিত শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি দেওয়া হলো:
(i) মাথার উপরে জ্বলিছে সূর্য।
* উপরে: অব্যয় (স্থানবাচক অব্যয়)
(ii) সুখ কে না চায়?
* সুখ: বিশেষ্য (গুণবাচক বিশেষ্য)
(iii) ম্লান আলোকে ফুটলি কেনো গোলক চাঁপার ফুল?
* ম্লান: বিশেষণ (আলোকের অবস্থা নির্দেশ করছে)
(iv) হে মহান, তোমাকে অভিবাদন!
* হে: অব্যয় (সম্বোধনবাচক অব্যয়)
(v) তোমায় দেখে প্রীত হলাম।
* প্রীত: বিশেষণ (অবস্থা নির্দেশ করছে)
(vi) কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।
* কোথাও: সর্বনাম (অনির্দিষ্ট স্থানবাচক সর্বনাম)
* হারিয়ে: অব্যয় (অসমাপিকা ক্রিয়া থেকে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত)
(vii) যথা ধর্ম, তথা জয়।
* যথা: অব্যয় (তুলনাবাচক অব্যয়)
* তথা: অব্যয় (তুলনাবাচক অব্যয়)
(viii) এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।
* এতক্ষণে: ক্রিয়া বিশেষণ (কহিলার সময় নির্দেশ করছে)
৪. (ক) উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর:
উপসর্গের সংজ্ঞা:
উপসর্গ হলো এমন কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ যা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটায়। উপসর্গের নিজস্ব কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু এরা যখন কোনো শব্দের আগে বসে, তখন তার অর্থের দ্যোতনা বা পরিবর্তন ঘটায়।
উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন:
১. প্র- (উত্তম, প্রকৃষ্ট অর্থে):
* প্র + হার = প্রহার (আঘাত করা)
* প্র + বচন = প্রবচন (উক্তি, প্রচলিত বাক্য)
২. পরা- (বিপরীত, সম্যক অর্থে):
* পরা + জয় = পরাজয় (হার)
* পরা + ক্রম = পরাক্রম (বীরত্ব)
৩. অপ- (মন্দ, বিপরীত অর্থে):
* অপ + মান = অপমান (অমর্যাদা)
* অপ + ব্যয় = অপব্যয় (অযথা খরচ)
৪. সম- (সম্যক, সম্যক অর্থে):
* সম + গীত = সঙ্গীত (গান)
* সম + পূর্ণ = সম্পূর্ণ (পুরো)
৫. বি- (বিশেষ, অভাব, গতি অর্থে):
* বি + জয় = বিজয় (জয়লাভ)
* বি + জ্ঞান = বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান)
৪. (খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে কোনো পাঁচটি):
সমাস হলো দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার প্রক্রিয়া, যার ফলে একটি নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়। নিচে প্রদত্ত শব্দগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করা হলো:
-
সোনারতরী:
-
ব্যাসবাক্য: সোনা নির্মিত তরী
-
সমাস: মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
-
-
সমন্বয়ক:
-
ব্যাসবাক্য: সম্যকরূপে অন্বয় করে যে
-
সমাস: উপপদ তৎপুরুষ সমাস
-
-
মহানবি:
-
ব্যাসবাক্য: মহান যে নবি
-
সমাস: সাধারণ কর্মধারয় সমাস
-
-
মূকাভিনয়:
-
ব্যাসবাক্য: মুখ দ্বারা অভিনয় (মুখের সাহায্যে অভিনয়)
-
সমাস: তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
-
-
গায়েহলুদ:
-
ব্যাসবাক্য: গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
-
সমাস: অলুক বহুব্রীহি সমাস
-
-
সেতার:
-
ব্যাসবাক্য: সে (তিন) তার যার
-
সমাস: দ্বিগু সমাস
-
-
ভবনদী:
-
ব্যাসবাক্য: ভব রূপ নদী
-
সমাস: রূপক কর্মধারয় সমাস
-
-
তোমরা:
-
ব্যাসবাক্য: তুমি ও রা (অনেকগুলো)
-
সমাস: নিত্য সমাস (এখানে 'তোমরা' একটি নিত্য সমাসের উদাহরণ, কারণ এর ব্যাসবাক্য হয় না বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।)
-
৫. (ক) বাক্য কাকে বলে? অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর:
বাক্য কাকে বলে?
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক পদের দ্বারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। বাক্যের একটি সম্পূর্ণ অর্থ থাকা আবশ্যক এবং এতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকা জরুরি (যদিও কখনও কখনও তা উহ্য থাকতে পারে)।
উদাহরণ:
-
আমি ভাত খাই।
-
মেয়েটি গান গায়।
অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ:
বক্তার মনোভাব বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে অর্থ অনুসারে বাক্যকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:
১. নির্দেশাত্মক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা কোনো ঘটনা, তথ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তাকে নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। এই বাক্য দুই প্রকারের হতে পারে:
* অস্তিবাচক (হ্যাঁ-সূচক): যখন কোনো ঘটনার অস্তিত্ব বা ইতিবাচকতা প্রকাশ পায়।
* উদাহরণ: সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।
* নেতিবাচক (না-সূচক): যখন কোনো ঘটনা বা তথ্যের অস্বীকৃতি বা নেতিবাচকতা প্রকাশ পায়।
* উদাহরণ: আমি মিথ্যা বলি না।
২. প্রশ্নবাচক বাক্য (প্রশ্নবোধক বাক্য): যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা প্রশ্ন করা হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে। এই বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) থাকে।
* উদাহরণ: তুমি কোথায় যাও?
৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, নিষেধ বা অনুমতি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।
* উদাহরণ: বইটি নিয়ে এসো (আদেশ)। বড়দের সম্মান করো (উপদেশ)। এক গ্লাস জল দাও (অনুরোধ)।
৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা বক্তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আশীর্বাদ বা শুভকামনা প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে।
* উদাহরণ: তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য (আবেগসূচক বাক্য): যে বাক্য দ্বারা বক্তার বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয় বা অন্য কোনো প্রবল আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। এই বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) থাকে।
* উদাহরণ: আহা, কী সুন্দর দৃশ্য! ছিঃ, কী নোংরা!
৫. (খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যান্তর কর (যে কোনো পাঁচটি):
বাক্যান্তর হলো বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে এক প্রকার বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করা। নিচে নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তরিত করা হলো:
(i) জয় হোক তব জয়। (নির্দেশাত্মক)
* রূপান্তরিত বাক্য: তোমার জয় হোক।
(ii) চলো ঘুরে আসি। (প্রশ্নবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: চলো কি ঘুরে আসি?
(iii) আমার বন্ধু হরিশ। (জটিল)
* রূপান্তরিত বাক্য: যিনি আমার বন্ধু, তিনি হরিশ।
(iv) লোকে যা বলে তাতে কান দিওনা। (যৌগিক)
* রূপান্তরিত বাক্য: লোকে যা বলে, এবং তুমি তাতে কান দিওনা।
(v) তুমি অধম, তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (সরল)
* রূপান্তরিত বাক্য: তুমি অধম হলেও আমি উত্তম হব।
(vi) দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: দেশের সেবা করো।
(vii) ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: কী সুন্দর ফুলটি!
(viii) ঘরে এলে খাতির করব না কেনো? (অস্তিবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: ঘরে এলে খাতির করবই।
৬. (ক) যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
বাক্য শুদ্ধিকরণ বলতে ব্যাকরণগত ত্রুটি, বানান ভুল, বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার পরিহার করে একটি বাক্যের সঠিক ও সুন্দর রূপ দেওয়াকে বোঝায়। নিচে প্রদত্ত বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো:
(i) সব পাখিই নীড় বাঁধে। (সমুদয় পক্ষীরাই-এর বদলে 'সব পাখিই' হবে, কারণ 'সমুদয়' এবং 'পক্ষীরাই' উভয়ই বহুবচন এবং এতে বাহুল্য দোষ ঘটেছে। 'পক্ষী'র বহুবচন 'পাখি' বেশি প্রচলিত।)
(ii) বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ('শ্রেষ্ঠতর' একটি ভুল প্রয়োগ; 'শ্রেষ্ঠ' নিজেই একটি উচ্চতর বিশেষণ, এর সাথে 'তর' যুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।)
(iii) বাক্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। ('উৎকর্ষতা' একটি ভুল প্রয়োগ; 'উৎকর্ষ' নিজেই বিশেষ্য পদ।)
(iv) ঐকতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। ('ঐক্যতান'-এর সঠিক বানান 'ঐকতান' হবে।)
(v) এক মাঘে শীত যায় না। ('পৌষ' মাসের বদলে 'মাঘ' হবে, কারণ এটি একটি প্রবাদ বাক্য এবং এর প্রচলিত রূপ 'এক মাঘে শীত যায় না'।)
(vi) ঘড়িটি হাতে দাও। ('ঘড়িকে' এখানে কারকগত ভুল; 'ঘড়িটি' হবে।)
(vii) মধুমিতা এমন রূপসী যেন অপ্সরা। ('অপ্সরী' একটি ভুল বানান; 'অপ্সরা' হবে।)
(viii) বাংলা বানান আয়ত্ত করা বেশ কঠিন। ('আয়ত্ব' একটি ভুল বানান; 'আয়ত্ত' হবে।)
৬. (খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করে লেখ:
অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভুল বানান, ব্যাকরণগত ত্রুটি এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ করে নিচে লেখা হলো:
জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে তাই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোনো মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে। মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে।
বিশ্লেষণ ও শুদ্ধিকরণ:
-
মনুসত্ত্ব মনুষ্যত্ব: সঠিক বানান।
-
রশ রস: সঠিক বানান।
-
সুন্দর্য্য সৌন্দর্য: সঠিক বানান।
-
খাইয়ে দাইয়ে খাইয়ে-দাইয়ে: এটি একটি দ্বিরুক্ত শব্দ, হাইফেন (-) ব্যবহার করে লেখা উচিত।
-
তুলবার জন্য নয়, ... উদ্দেশ্য তোলবার জন্য নয়, ... উদ্দেশ্যে: বাক্যের শেষে 'উদ্দেশ্যে' ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যা 'উদ্দেশ্য' থেকে এসেছে।
৭. (ক) যেকোনো দশটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ:
পারিভাষিক শব্দ হলো নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র বা বিষয়ে ব্যবহৃত বিশেষ অর্থবহ শব্দ। নিচে প্রদত্ত ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক রূপ দেওয়া হলো:
-
Optional: ঐচ্ছিক
-
File: নথি / ফাইল
-
Equation: সমীকরণ
-
Radio: বেতার
-
Training: প্রশিক্ষণ
-
Graduate: স্নাতক
-
Secretary: সচিব
-
Forecast: পূর্বাভাস
-
Nebula: নীহারিকা
-
Quota: কোটা / বরাদ্দ
-
Theory: তত্ত্ব
-
Tax: কর
-
Note: টীকা / নোট
-
Myth: পুরাণকথা / উপকথা
-
Galaxy: ছায়াপথ
৭. (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ:
A patriot is a man who loves his country, works for it and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.
অনুবাদ:
দেশপ্রেমিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, এর জন্য কাজ করেন এবং এর জন্য যুদ্ধ করতে ও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন। প্রতিটি সৈনিকই তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য, কিন্তু সেরা সৈনিকরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে। তারা দেশকে ভালোবাসে বলেই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। তারাই জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।
৮. (ক) তোমার এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বরাতের একটি দিনলিপি:
২৭শে জুন, ২০২৫, বৃহস্পতিবার
রাত ১১:৪৫টা
আজ রাতটা অন্যরকম, আর কিছুক্ষণ পরেই ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গেলেই জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে – এইচ.এস.সি. পরীক্ষা। কাল সকাল ৯টায় প্রথম পরীক্ষা, বাংলা প্রথম পত্র। সারাদিন ধরে একটা চাপা উত্তেজনা আর ভয় কাজ করছিল। যদিও পড়াশোনায় কোনো কমতি রাখিনি, তবুও অজানা একটা দুশ্চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরেছি। বারবার বইয়ের পাতা উল্টে দেখেছি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। বাবা-মা দুজনেই খুব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। মা নিজ হাতে আমার পছন্দের খাবার রান্না করে খাইয়েছেন, আর বাবা আমার পাশে বসে পরীক্ষার কিছু কৌশল নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের চোখে মুখেও আমার জন্য একরকম চিন্তা স্পষ্ট।
রাত বাড়ার সাথে সাথে পরিবেশটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে। রাস্তার কোলাহলও কমে এসেছে। টেবিলে শুধু আমার বইগুলো আর পরীক্ষার প্রবেশপত্রটা পড়ে আছে। মনে পড়ছে গত দু'বছরের পড়াশোনার কথা, ক্লাসের বন্ধুদের কথা, স্যারদের উপদেশগুলো। কত স্বপ্ন, কত আশা জড়িয়ে আছে এই পরীক্ষার সাথে। ভালো ফলাফল করে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্নটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আজ রাতে।
ঘুম আসছে না ঠিকমতো। তবুও চেষ্টা করছি মনকে শান্ত রাখতে। জানি, দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। যা প্রস্তুতি নেওয়ার তা তো নেওয়া হয়েই গেছে। এখন শুধু নিজেকে স্থির রেখে পরীক্ষাটা ভালোভাবে দিতে হবে। নিজেকে বারবার বলছি, "আমি পারবো, আমি পারবো।" প্রার্থনা করছি যেন কালকের দিনটা ভালো যায়। সময় হয়েছে বিছানায় যাওয়ার, অন্তত একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শুভরাত্রি, আমার স্বপ্ন পূরণের যাত্রার পূর্বরাত!
৮. (খ) 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ' শীর্ষক প্রতিবেদন:
প্রতিবেদন
পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ: অপরিহার্যতা ও করণীয়
তারিখ: ২৯শে জুন, ২০২৫
স্থান: চট্টগ্রাম
ভূমিকা:
পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়ের ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্যের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বৃক্ষরোপণ একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
পরিবেশগত ভারসাম্যে বৃক্ষের ভূমিকা:
বৃক্ষ আমাদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এর ভূমিকা অনস্বীকার্য:
-
অক্সিজেন উৎপাদন: গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা প্রাণিকুলের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য।
-
কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ: গাছ বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমাতে সাহায্য করে। এটি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
-
ভূমি ক্ষয় রোধ: গাছের শিকড় মাটি ধরে রাখে, ফলে বন্যা ও বৃষ্টির কারণে ভূমি ক্ষয় রোধ হয়।
-
বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ: বৃক্ষ ঘন বনাঞ্চল তৈরি করে মেঘ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে।
-
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: গাছপালা ছায়া প্রদান করে এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিবেশের তাপমাত্রা শীতল রাখে।
-
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: বনভূমি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল, যা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে।
-
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ও ভূমিক্ষয় মোকাবিলায় বৃক্ষরাজি প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে।
বর্তমান পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ:
বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পায়ন, এবং কৃষিজমির সম্প্রসারণের কারণে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন চলছে। বনভূমি উজাড় হচ্ছে এবং নতুন বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বাড়ছে, যেমন – খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, এবং লবণাক্ততা।
করণীয়:
পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:
-
ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা।
-
বনভূমি সংরক্ষণ: বিদ্যমান বনভূমি কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা।
-
জনসচেতনতা বৃদ্ধি: বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং পরিবেশ রক্ষায় এর ভূমিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃক্ষরোপণের আগ্রহ সৃষ্টি করা।
-
ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের রোপণ: পরিবেশের উপকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত সুবিধা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করা।
-
শহরাঞ্চলে সবুজায়ন: শহরের ছাদে বাগান করা, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো এবং পরিত্যক্ত স্থানগুলোকে সবুজে পরিণত করা।
-
আইনের কঠোর প্রয়োগ: বৃক্ষনিধন ও বনভূমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
-
সামাজিক বনায়ন: স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া, যাতে তারা নিজেদের রোপিত গাছের মালিকানা ও সুবিধা ভোগ করতে পারে।
উপসংহার:
পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা কেবল একটি পরিবেশগত বিষয় নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। বৃক্ষরোপণ এই ভারসাম্য রক্ষায় একটি সহজ এবং কার্যকর উপায়। আসুন, আমরা সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে গাছ লাগানোর এবং এর পরিচর্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করি, যাতে একটি সবুজ ও সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারি।
৯. (ক) ফেসবুকে অধিক সময় না দেওয়ার জন্য ছোটভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি:
বিষয়: ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় নষ্ট না করার অনুরোধ
প্রিয় [ছোটভাইয়ের নাম],
কেমন আছিস? আশা করি ভালো আছিস। আজকাল তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই ফেসবুকে অনেক বেশি সময় ব্যয় করছিস। তোর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত।
ফেসবুক বা অন্য যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভালো লাগার জিনিস, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বন্ধুদের সাথে যুক্ত থাকা, খবর জানা, বা বিনোদন—সবকিছুই এতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন এটি আমাদের সময়ের একটা বড় অংশ গ্রাস করে নেয় এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজ, বিশেষ করে পড়াশোনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তখন তা সমস্যার কারণ হয়।
মনে রাখিস, এখন তোর এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের ভিত্তি তৈরি হয় এই সময়ে। যদি তুই এখন সময় নষ্ট করিস, তাহলে পরে আফসোস করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজ যেমন বই পড়া, খেলাধুলা করা, বা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা কর। এগুলো তোকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ রাখবে।
আমি জানি তুই বুদ্ধিমান এবং তোর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। শুধু একটু মনোযোগ আর সময় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। তাই অনুরোধ করছি, ফেসবুকে সময় কাটানোটা একটু কমা এবং পড়াশোনার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হ।
যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাকে জানাবি। আমি সব সময় তোর পাশে আছি।
তোর ভালো চাই।
শুভেচ্ছান্তে,
[তোর নাম]
[তোর ই-মেইল আইডি]
৯. (খ) ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পৌরসভা মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র:
বরাবর
মেয়র/চেয়ারম্যান,
[পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের নাম] পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ,
[এলাকার নাম], [জেলা]
বিষয়: এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।
জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি [আপনার নাম], [এলাকার নাম]-এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। সম্প্রতি আমাদের এলাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে, যা এলাকার জনমনে গভীর উদ্বেগ ও ভয়ের সৃষ্টি করেছে।
বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে মশার প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ড্রেনগুলো অপরিষ্কার থাকায় এবং যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলায় মশার উপদ্রব আরও বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে মশা নিধনে কার্যকর পদক্ষেপ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।
এমতাবস্থায়, আপনার নিকট বিনীত আবেদন, এলাকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে নিম্নলিখিত জরুরি ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে আমাদের এলাকাবাসীকে এই ভয়াবহ রোগ থেকে রক্ষা করতে আপনার সদয় মর্জি হয়:
১. নিয়মিত মশা নিধনের জন্য ফগার মেশিন দ্বারা মশার ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা।
২. এলাকার সকল ড্রেন ও নালা দ্রুত পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. জমে থাকা পানি অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৪. ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
আপনার দ্রুত পদক্ষেপ আমাদের এলাকার হাজার হাজার মানুষকে ডেঙ্গুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে।
বিনীত নিবেদক,
[আপনার নাম]
[আপনার ঠিকানা]
[আপনার মোবাইল নম্বর]
[তারিখ]
১০. (ক) সারমর্ম:
মূল ভাব: নবজাতকের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। পৃথিবীর অতীতের ব্যর্থতা, ধ্বংসাবশেষ ও জঞ্জাল দূর করে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ রেখে যাওয়ার অঙ্গীকারই এই কবিতার মূল বার্তা।
সারমর্ম:
নব প্রজন্মের আগমনে পুরাতন ও জীর্ণ পৃথিবীকে নবজীবন দানের প্রয়াস এক মানবিক অঙ্গীকার। পূর্বসূরিদের ব্যর্থতা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে নতুন শিশুর জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব আমাদেরই। যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন এই পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ করে তোলার দৃঢ় সংকল্পই যেন আমাদের জীবনের মূল ব্রত হয়।
১০. (খ) ভাব-সম্প্রসারণ: "প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।"
ভাব-সম্প্রসারণ:
"প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না" — এই উক্তিটি মানব অস্তিত্বের গভীর অর্থ এবং মননশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে। কেবল জৈবিক অস্তিত্বই মানুষের পরিচয় নয়; মানুষের মন, তার বিবেক, বুদ্ধি, আবেগ, সংবেদনশীলতা এবং নৈতিক মূল্যবোধই তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী বাস করে, যাদের সকলেরই প্রাণ আছে। তারা জন্মায়, খায়, ঘুমায়, বংশবৃদ্ধি করে এবং একসময় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জীবনচক্র মূলত জৈবিক চাহিদা এবং সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। এই প্রাণীজগতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মানুষেরও প্রাণ আছে এবং সেও মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে। এই অর্থে, মানুষও একটি প্রাণী।
তবে মানুষের একটি বিশেষ দিক হলো তার মন। এই মন কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের আছে বিচার-বুদ্ধি, আত্ম-উপলব্ধি, সৃজনশীলতা, সহানুভূতি, প্রেম, ঘৃণা, দয়া, মায়া, এবং ন্যায়-অন্যায়ের বোধ। মানুষ অতীত থেকে শেখে, ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করে। সে জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারে, শিল্প-সাহিত্য রচনা করতে পারে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। সর্বোপরি, মানুষ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে এবং নৈতিকতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। এই সমস্ত গুণাবলিই মানুষের মন থেকে উৎসারিত, যা তাকে কেবলমাত্র একটি জৈবিক সত্তা থেকে এক উচ্চতর, মননশীল সত্তায় পরিণত করে।
যখন কোনো ব্যক্তি এই মানবিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলে, যখন সে কেবল তার সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়, তখন তার জৈবিক অস্তিত্ব থাকলেও 'মানুষ' হিসেবে তার সার্থকতা বিলুপ্ত হয়। বিবেকহীনতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি দেখা যায় যারা কেবল নিজের লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করে, যারা কোনো মানবিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা করে না। তাদের প্রাণ থাকলেও মন অনুপস্থিত।
সুতরাং, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার দেহ বা প্রাণের মধ্যে নিহিত নয়, বরং তার মন ও মননশীলতার মধ্যে নিহিত। এই মনই মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তাকে উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত করে। মানুষের মানবিকতা তখনই পূর্ণতা পায় যখন তার প্রাণ এবং মনের মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটে।
১১. (ক) সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন:
[স্থান: শহরের একটি চায়ের দোকান]
[সময়: সন্ধ্যা ৬:৩০]
রাজু: কিরে রানা, মুখটা এমন শুকনো কেন? কী হয়েছে?
রানা: আর বলিস না দোস্ত, আজ সকালে একটা ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা দেখলাম। চোখের সামনে সব ঘটল।
রাজু: বলিস কী! কোথায়, কীভাবে ঘটল?
রানা: আমাদের কলেজ মোড়ের কাছেই। একটা দ্রুতগামী বাস ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটা রিকশাকে চাপা দিল। রিকশার চালক আর একজন যাত্রী তো ঘটনাস্থলেই... [আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে]
রাজু: ওহ নো! খুব খারাপ খবর তো। আজকাল সড়ক দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত প্রাণ যাচ্ছে, তবুও যেন কারো হুঁশ ফিরছে না।
রানা: ঠিক বলেছিস। দুর্ঘটনার মূল কারণগুলো তো সবারই জানা। বেপরোয়া গতি, ট্রাফিক আইন না মানা, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন গাড়ি—এগুলোই তো প্রধান সমস্যা।
রাজু: শুধু এগুলোই নয়। যাত্রী-সাধারণের অসচেতনতাও কম দায়ী নয়। ফুটপাত ব্যবহার না করে রাস্তা দিয়ে হাঁটা, চলন্ত বাসে ওঠা-নামা করা, মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হওয়া—এগুলোও দুর্ঘটনার কারণ হয়।
রানা: একদম ঠিক। আমি প্রায়ই দেখি, তরুণ মোটরসাইকেল আরোহীরা হেলমেট না পরেই দ্রুত গতিতে বাইক চালায়। অনেক সময় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেও দেখা যায়, যা খুবই বিপজ্জনক।
রাজু: আর আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থার কথা কী বলবি! অনেক সময় ট্রাফিক পুলিশকে তাদের দায়িত্ব পালনে উদাসীন দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রভাব বা আর্থিক লেনদেনের কারণে অনেক সময় দুর্বল গাড়িও রাস্তায় চলতে পারে।
রানা: এই সমস্যা সমাধানের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ট্রাফিক আইনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, চালকদের প্রশিক্ষণ আরও উন্নত করতে হবে এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায় নামানো বন্ধ করতে হবে।
রাজু: জনসচেতনতাও খুব জরুরি। গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার চালাতে হবে, যাতে মানুষ ট্রাফিক আইন মানতে এবং সাবধানে চলাফেরা করতে আগ্রহী হয়। স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।
রানা: তোর সাথে আমি একমত। আমরা যদি সবাই সচেতন হই এবং নিয়ম মেনে চলি, তাহলে এই সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। সরকার, পরিবহন মালিক, চালক, যাত্রী—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে।
রাজু: হ্যাঁ রে দোস্ত। এসব দেখে সত্যিই খুব খারাপ লাগে। আর যেন একটিও প্রাণ সড়কে ঝরে না পড়ে, এই কামনা করি।
রানা: চল, আজ আমরা শপথ করি যে, আমরা নিজেরা সবসময় ট্রাফিক আইন মেনে চলব এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে সচেতন করব।
রাজু: অবশ্যই! এটাই হবে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।
১১. (খ) প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি খুদে গল্প:
লোভের পরিণাম
স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শামীম তার নিজের এক চিলতে জমিতে একটি ফলের বাগান করার সিদ্ধান্ত নিল। সে শুধু আম, জাম বা লিচুর মতো ফল নয়, বরং নতুন প্রজাতির ড্রাগন ফল চাষের পরিকল্পনা করল। প্রথমে গ্রামের মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করল, "এসব বিদেশি ফল এদেশে হবে নাকি! ধান-পাট ছেড়ে ফলের বাগান!" কিন্তু শামীম কারো কথায় কান দিল না। সে নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমে তার বাগানে ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করল।
প্রথম বছর ফলন তেমন ভালো হলো না, তবে দ্বিতীয় বছর থেকে বাগান ভরে উঠল টকটকে লাল ড্রাগন ফলে। বাজারে ড্রাগন ফলের চাহিদা তখন আকাশচুম্বী, আর শামীম হয়ে উঠল গ্রামের সবচেয়ে ধনী কৃষক। তার ড্রাগন ফল দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন সুস্বাদু। তার এই সাফল্যে গ্রামের অন্যান্য কৃষকরা অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাছে পরামর্শ নিতে আসত। শামীম সানন্দে তাদের সাহায্য করত, কারণ সে চাইত সবাই স্বাবলম্বী হোক।
কিন্তু মানুষের লোভ বড়ই অদ্ভুত জিনিস। শামীমের এই অভাবনীয় সাফল্য দেখে গ্রামের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, রহমান, যার কৃষিকাজ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না, সেও রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। রহমান তার সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে এবং সুদে টাকা নিয়ে একটি বিশাল ড্রাগন ফলের বাগান তৈরি করল। সে শামীমের চেয়েও বড় হতে চাইল, একাই সমস্ত বাজার দখল করার নেশা তাকে পেয়ে বসল। সে ভাবল, যত বেশি ফল তত বেশি লাভ, তাই শামীমের থেকে বেশি ফলন পেতে সে জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে শুরু করল, যা মাটির জন্য ক্ষতিকর ছিল।
প্রথম বছর রহমানের ফলন শামীমের চেয়েও বেশি হলো। কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে তার ফলের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল, ফলগুলো আকারেও ছোট হতে শুরু করল এবং সেগুলো তাড়াতাড়ি পচে যেত। বাজারে তার ফলের দাম পড়ে গেল। ক্রেতারা একবার কিনে প্রতারিত হওয়ার পর আর রহমানের ফল কিনতে চাইল না। এদিকে অতিরিক্ত রাসায়নিকের কারণে তার জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার বাগান মরে যেতে শুরু করল এবং সে ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ল।
রহমান যখন তার সব হারিয়ে দিশেহারা, তখন সে বুঝতে পারল, পরিশ্রমের ফল মিষ্টি হলেও লোভের ফল সবসময়ই বিষাক্ত। শামীমের নিষ্ঠা ও সততা তাকে সফল করেছিল, আর রহমানের অদম্য লোভই তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল।
১২. (খ) মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:
মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: এক অবিস্মরণীয় অগ্রগতি
সভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই মানবজাতি জ্ঞান অর্জনের নেশায় মহন। এই জ্ঞান সাধনার ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞান, আর সেই বিজ্ঞানের প্রয়োগিক রূপ হলো প্রযুক্তি। আজকের আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এতটাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একটিকে ছাড়া অন্যটির কথা কল্পনাও করা যায় না। মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম; এটি আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ, সুন্দর ও গতিময়।
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় বিপ্লব:
মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে আনা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আজ আর অজানা রোগে অকালে প্রাণহানি ঘটে না। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার, টিকাকরণ কর্মসূচি, জটিল রোগের নির্ভুল নির্ণয় পদ্ধতি (যেমন: এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই), অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপন—এসবই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি আজ নিরাময়যোগ্য। প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে বসেই স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্যও আশার আলো দেখিয়েছে।
যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার:
যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান আমাদের বিশ্বকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। একসময় চিঠি লিখে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতো, আজ মুহূর্তেই ই-মেইল, হোয়াটসঅ্যাপ বা ভিডিও কলের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কৃত্রিম উপগ্রহ, ফাইবার অপটিক কেবল—এগুলো শুধু যোগাযোগকে দ্রুত করেনি, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। মানুষ এখন ঘরে বসেই বিশ্বের যেকোনো তথ্য জানতে পারছে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে এবং বিনোদন উপভোগ করতে পারছে। তথ্যপ্রযুক্তি আজ বিশ্বকে একটি 'বৈশ্বিক গ্রামে' পরিণত করেছে।
কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় অগ্রগতি:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষিক্ষেত্রেও এসেছে অভাবনীয় উন্নতি। উচ্চ ফলনশীল বীজ, উন্নত সার, আধুনিক সেচ পদ্ধতি, কীটনাশক এবং উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার খাদ্য উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। জিন প্রকৌশল ও বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক ও পুষ্টিকর ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে এবং অপুষ্টি দূরীকরণে সহায়তা করছে।
শিল্প ও পরিবহনের উন্নয়ন:
শিল্প ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে করেছে দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় মেশিনপত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিবহনেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দ্রুতগামী ট্রেন, আধুনিক বিমান, জাহাজ, এবং উন্নত মোটরগাড়ি মানুষকে দ্রুততম সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। মহাকাশ বিজ্ঞান এবং রকেট প্রযুক্তি মানুষকে পৃথিবীর বাইরেও পাড়ি জমানোর সুযোগ করে দিয়েছে।
শিক্ষা ও গবেষণায় নতুন দিগন্ত:
শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ইন্টারনেট, অনলাইন লাইব্রেরি, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল ক্লাসরুম শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের অফুরন্ত সুযোগ তৈরি করেছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করছে এবং মানবজাতির অজানাকে জানার আগ্রহকে পূরণ করছে।
উপসংহার:
মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সত্যিই অপরিসীম। এটি মানুষের জীবনকে আরামদায়ক, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ করেছে। তবে এর অপব্যবহার পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক যুদ্ধ, এবং সামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যার জন্ম দিতে পারে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ও নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে এটি মানবজাতির জন্য কেবল আশীর্বাদ বয়ে আনে, অভিশাপ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই আমরা একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।