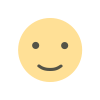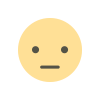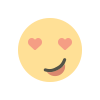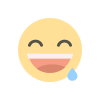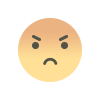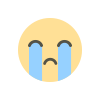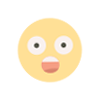এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। ঢাকা বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। ঢাকা বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
(১)
(ক) উদাহরণসহ 'অ' ধ্বনির উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
বাংলায় 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ প্রধানত দু'রকমের হয়: সংবৃত ('ও'-কারের মতো) এবং বিবৃত ('অ'-কারের মতো)। এখানে 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ দেওয়া হলো:
১. শব্দের আদিতে 'অ': শব্দের শুরুতে থাকা 'অ' ধ্বনির পরে যদি ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ক্ষ, জ্ঞ, য-ফলা, র-ফলা, বা ল-ফলা থাকে, তবে সেই 'অ' সংবৃত বা 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ:
* অতি (ওতি)
* অদূর (ওদুর)
* অক্ষ (ওক্খো)
* প্রত্যয় (প্রোত্ তয়্)
২. দ্বিতীয় 'অ' ধ্বনি: শব্দের দ্বিতীয় 'অ' ধ্বনির পরে যদি ই-কার বা উ-কার থাকে, তবে প্রথম 'অ' ধ্বনিটি সংবৃত হয়।
* উদাহরণ:
* কঠিন (কোঠিন)
* মধুর (মোধুর)
৩. নঞর্থক 'অ': নঞর্থক উপসর্গ 'অ' বা 'অন' যুক্ত শব্দে 'অ' ধ্বনি বিবৃত হয় (অর্থাৎ 'অ' রূপেই উচ্চারিত হয়)।
* উদাহরণ:
* অকাল (অকাল)
* অজানা (অজানা)
৪. যুক্তব্যঞ্জনে 'অ': যুক্তব্যঞ্জনের পরে যদি 'অ' ধ্বনি থাকে এবং তা শব্দের শেষে না হয়, তবে সেই 'অ' প্রায়শই বিবৃত থাকে।
* উদাহরণ:
* কলম (কলম)
* জল (জল্)
৫. শব্দের শেষে 'অ': শব্দের শেষে যদি 'অ' ধ্বনি থাকে, তবে সেই 'অ' সাধারণত সংবৃত বা 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ:
* ফল (ফল্-ও)
* করল (কর্-লো)
(খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ:
এখানে প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ দেওয়া হলো:
-
অধ্যক্ষ: ওদ্ধোক্খো
-
ইতোমধ্যে: ইতোমোদ্ধে
-
উদ্যোগ: উদোগ্
-
ঐকতান: ওইকোতান্
-
কল্যাণ: কোল্-লান
-
চর্যাপদ: চোর্যাপদ
-
ধন্যবাদ: ধোন্ নবাদ্
-
পদ্ম: পোদ্-দো
(২)
(ক) উদাহরণসহ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলী থেকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ নিচে দেওয়া হলো:
১. ই-কার / ঈ-কার ব্যবহার: সকল অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র) শব্দে কেবল ই-কার (ি) ব্যবহৃত হবে। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত বানান অপরিবর্তিত থাকবে।
* উদাহরণ:
* সরকারি, বিদেশি, আসামি, দিদি (সঠিক)
* বিদেশী, আসামী, দিদী (ভুল)
২. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম বজায় থাকবে। তবে, অতৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ (ণ) ও মূর্ধন্য-ষ (ষ) ব্যবহৃত হবে না, কেবল দন্ত্য-ন (ন) ও দন্ত্য-স (স) ব্যবহৃত হবে।
* উদাহরণ:
* তৎসম: কারণ, উষ্ণ, কষ্ট (সঠিক)
* অতৎসম: কুরআন, জার্মান, পোশাক (সঠিক)
* কোরআন, জার্মাণ, পোষাক (ভুল)
৩. বিসর্গ (ঃ) বর্জন: অ-তৎসম শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জনীয়। এছাড়া, অব্যয় পদে (বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলেও) বিসর্গ ব্যবহৃত হবে না।
* উদাহরণ:
* বিশেষত, কার্যত, প্রধানত, মূলত (সঠিক)
* বিশেষতঃ, কার্যতঃ, প্রধানতঃ, মূলতঃ (ভুল)
* (তবে, তৎসম শব্দ 'দুঃখ' - এখানে বিসর্গ থাকবে)
৪. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন: তৎসম ও অতৎসম উভয় প্রকার শব্দেই রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।
* উদাহরণ:
* কর্ম, কার্য, সূর্য, অর্চনা (সঠিক)
* কর্ম্ম, কার্য্য, সূর্য্য, অর্চ্চণা (ভুল)
৫. অনুস্বার (ং) ও ঙ (অ)-এর ব্যবহার: বাংলা শব্দে যেখানে ক-বর্গীয় ধ্বনির আগে ঙ থাকে, সেখানে ঙ বসবে। অন্যথায় অনুস্বার (ং) বসবে। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা হবে।
* উদাহরণ:
* রং, বাংলা, সঙ্গ (সঠিক)
* রঙ্গ, বাঙলা, সঙ্ঘ (ভুল)
* ইংলিশ (সঠিক)
(খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:
এখানে প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ বানান দেওয়া হলো:
-
অধ্যায়ন: অধ্যয়ন
-
অপরাহ্ন: অপরাহ্ণ
-
আমাবস্যা: অমাবস্যা
-
গ্রামীন: গ্রামীণ
-
দন্ডবিদি: দণ্ডবিধি
-
প্রতিযোগীতা: প্রতিযোগিতা
-
বিভিসিকা: বিভীষিকা
-
রেজিষ্ট্রেশন: রেজিস্ট্রেশন
(৩)
(ক) উদাহরণসহ ক্রিয়া পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা, ঘটা বা কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া বোঝায়, তাকে ক্রিয়া পদ বলে। এটি বাক্যের অপরিহার্য অংশ এবং বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে।
ক্রিয়া পদকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে কয়েকটি প্রধান শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ:
* **সকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায়, তবে তা সকর্মক ক্রিয়া।
* **উদাহরণ:** আমি **ভাত খাই**। (কী খাই? – ভাত)
* সে **বই পড়ছে**। (কী পড়ছে? – বই)
* **অকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
* **উদাহরণ:** ছেলেটি **ঘুমায়**।
* পাখি **উড়ছে**।
* **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে (একটি মুখ্য কর্ম ও একটি গৌণ কর্ম), তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। সাধারণত ব্যক্তিবাচক কর্ম গৌণ কর্ম এবং বস্তুবোচক কর্ম মুখ্য কর্ম হয়।
* **উদাহরণ:** মা **শিশুকে চাঁদ দেখালেন**। (কাকে দেখালেন? – শিশুকে; কী দেখালেন? – চাঁদ)
* শিক্ষক **ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন**। (কাকে শেখাচ্ছেন? – ছাত্রদের; কী শেখাচ্ছেন? – ব্যাকরণ)
২. গঠন অনুসারে ক্রিয়াপদ:
* **মৌলিক ক্রিয়া (একক ক্রিয়া):** যে ক্রিয়াকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে। এটি ধাতু থেকে গঠিত হয়।
* **উদাহরণ:** সে **যায়**, আমি **করি**, তুমি **পড়**।
* **সাধিত ক্রিয়া:** একাধিক অংশ দ্বারা গঠিত ক্রিয়াকে সাধিত ক্রিয়া বলে। এটি মূলত দুটি উপায়ে গঠিত হতে পারে:
* **নামধাতু থেকে গঠিত ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকরণ অব্যয়ের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে নামধাতু বলে এবং তার থেকে গঠিত ক্রিয়াকে নামধাতু থেকে গঠিত ক্রিয়া বলে।
* **উদাহরণ:** আমি তোমাকে **বেতাচ্ছি** (বেত + আ)।
* ছেলেটি **ঘুমাচ্ছে** (ঘুম + আ)।
* **প্রযোজক ক্রিয়া:** কর্তা যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করায়, তখন সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
* **উদাহরণ:** মা **শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন**। (মা নিজে দেখছেন না, শিশুকে দেখাচ্ছেন)
* শিক্ষক **ছাত্রদের পড়াচ্ছেন**।
* **যৌগিক ক্রিয়া (মিশ্র ক্রিয়া):** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কৃদন্ত বা সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়ায় দুইটি ক্রিয়াপদ থাকে, যার একটি সমাপিকা ও অন্যটি অসমাপিকা।
* **উদাহরণ:** সে **কাজটা করে ফেলল**। (করে – অসমাপিকা, ফেলল – সমাপিকা)
* তার কথা **শুনে রাখো**।
* **যৌগিক ক্রিয়া (Composite Verb):** একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত হয় এবং বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।
* **উদাহরণ:** সে **খেয়ে ফেলল**।
* ছেলেটি **হাসতে লাগল**।
৩. ভাব অনুসারে ক্রিয়াপদ:
* **সমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে এবং বক্তার মনোভাব পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
* **উদাহরণ:** আমি **ভাত খাই**।
* সে **স্কুলে যায়**।
* **অসমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না এবং আরও কিছু শোনার বা বলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া সাধারণত 'ইয়া', 'ইলে', 'ইলে', 'লে', 'তে' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।
* **উদাহরণ:** আমি **ভাত খেয়ে** বাজারে যাব। (খেয়ে – অসমাপিকা)
* সে **বই পড়ে** ঘুমাল। (পড়ে – অসমাপিকা)
৪. অন্যান্য প্রকার:
* **অসমর্থক ক্রিয়া (Auxiliary Verb):** মূল ক্রিয়ার অর্থ স্পষ্ট করতে যে ক্রিয়া সাহায্য করে।
* **উদাহরণ:** সে কাজটি **করছে**। (করা - মূল, করছে - অসমর্থক)
* **অব্যয় ক্রিয়া:** কিছু ক্রিয়া অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন - থাকা, হওয়া।
* **উদাহরণ:** সে এখানে **থাকত**।
(খ) নিম্নরেখ যে-কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর:
(i) পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।
* বাঙালির: বিশেষ্য (জাতিবাচক বিশেষ্য) / বিশেষণ (সম্বন্ধ পদ, বিশেষ্যের গুণ নির্দেশক)
(ii) আজ নয় কাল সে আসবেই।
* নয়: অব্যয় (নঞর্থক অব্যয়)
(iii) হে বন্ধু, বিদায়।
* হে: অব্যয় (সম্বোধনবাচক অব্যয়)
(iv) তুমি যে আমার কবিতা।
* কবিতা: বিশেষ্য (সাধারণ বিশেষ্য)
(v) মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা।
* গরব: বিশেষ্য (গুণবাচক বিশেষ্য)
(vi) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
* দুঃখ: বিশেষ্য (গুণবাচক বিশেষ্য / ভাববাচক বিশেষ্য)
(vii) আমিন ও সামিন দুই ভাই।
* ও: অব্যয় (সংযোজক অব্যয়)
(viii) এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।
* মিছিল: বিশেষ্য (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য)
(৪)
(ক) বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
উপসর্গ হলো কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ যা ধাতু বা নামপদের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন ঘটায়। উপসর্গের নিজস্ব কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু শব্দের আগে যুক্ত হলে এরা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা:
বাংলা ভাষায় উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর প্রধান কারণগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:
১. নতুন শব্দ গঠন: উপসর্গ বাংলা শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার একটি অন্যতম প্রধান উপায়। একই মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের নতুন শব্দ তৈরি করা যায়। এটি ভাষার গতিশীলতা বাড়ায় এবং নতুন নতুন ধারণা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।
* উদাহরণ: 'হার' একটি শব্দ যার অর্থ পরাজয় বা গলার হার। এর সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করে ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়:
* আ-হার (খাওয়া)
* প্র-হার (মার)
* বি-হার (ভ্রমণ)
* উপ-হার (ভেট)
* পরি-হার (ত্যাগ)
২. শব্দের অর্থের পরিবর্তন: উপসর্গ শব্দের মূল অর্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে একটি নতুন বা বিপরীত অর্থ দান করতে পারে।
* উদাহরণ: 'পূর্ণ' শব্দের অর্থ 'ভরা'। কিন্তু 'পরি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ (সম্পূর্ণ ভরা) বা 'অ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে অপূর্ণ (সম্পেজ্বল নয়) অর্থ প্রকাশ করে।
* 'দান' শব্দের অর্থ 'দেওয়া'। 'প্র' উপসর্গ যোগ করে প্রধান (মুখ্য) বা 'অ' উপসর্গ যোগ করে অদান (না দেওয়া)।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ: কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপসর্গ শব্দের মূল অর্থকে আরও বিস্তৃত বা প্রসারিত করে।
* উদাহরণ: 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'জানা'। 'বি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষরূপে জানা) অর্থ প্রকাশ করে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন: আবার কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ শব্দের অর্থকে সংকুচিত বা সুনির্দিষ্ট করে।
* উদাহরণ: 'কাল' শব্দের অর্থ 'সময়'। 'সু' উপসর্গ যুক্ত হয়ে সুসময় (ভালো সময়) অর্থ প্রকাশ করে।
৫. বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য: উপসর্গের প্রয়োগ বাক্যে শ্রুতিমাধুর্য ও অর্থের গভীরতা বাড়ায়। এটি ভাষার প্রকাশভঙ্গিকে আরও সুনির্দিষ্ট, কার্যকর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে, যা সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৬. পদমর্যাদা পরিবর্তন: কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ নতুন শব্দ তৈরির মাধ্যমে পদের ব্যাকরণিক শ্রেণি পরিবর্তন করতে পারে, যদিও এটি সরাসরি উপসর্গের মূল কাজ নয়।
সংক্ষেপে, উপসর্গ বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারকে অগণিত নতুন শব্দ দিয়ে সমৃদ্ধ করে, শব্দের অর্থের বহুমুখিতা আনে এবং ভাষার প্রকাশভঙ্গিকে আরও কার্যকর ও সুন্দর করে তোলে। এটি ভাষার প্রাণবন্ততা ও নমনীয়তা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
(খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:
এখানে প্রদত্ত সকল শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করা হলো:
১. কাগজ-কলম
* ব্যাসবাক্য: কাগজ ও কলম
* সমাস: দ্বন্দ্ব সমাস
২. তেপান্তর
* ব্যাসবাক্য: তিন প্রান্তরের সমাহার
* সমাস: দ্বিগু সমাস
৩. নবীনবরণ
* ব্যাসবাক্য: নবীনকে বরণ
* সমাস: চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস (বা সম্প্রদান তৎপুরুষ সমাস)
৪. মুখচন্দ্র
* ব্যাসবাক্য: মুখ চন্দ্রের ন্যায় (সুন্দর)
* সমাস: উপমান কর্মধারয় সমাস (অথবা মুখরূপ চন্দ্র - রূপক কর্মধারয় সমাস)
৫. গণশিক্ষা
* ব্যাসবাক্য: গণ (সাধারণ মানুষ) এর শিক্ষা
* সমাস: ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৬. বনবাস
* ব্যাসবাক্য: বনে বাস
* সমাস: সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
৭. সিংহাসন
* ব্যাসবাক্য: সিংহ চিহ্নিত আসন
* সমাস: মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
৮. কাজলকালো
* ব্যাসবাক্য: কাজলের ন্যায় কালো
- সমাস: উপমান কর্মধারয় সমাস
(৫)
(ক) বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
গঠনগতভাবে বাক্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল বাক্য, জটিল বাক্য (বা মিশ্র বাক্য) এবং যৌগিক বাক্য।
১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি মাত্র কর্তা থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। এটি একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।
* উদাহরণ:
* ছেলেটি বই পড়ে।
* বৃষ্টি হচ্ছে।
* সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।
২. জটিল বাক্য (মিশ্র বাক্য): যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলো সাধারণত 'যে', 'যিনি', 'যা', 'যখন', 'যদি', 'যদিও' ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয় দিয়ে শুরু হয়।
* উদাহরণ:
* যে কঠোর পরিশ্রম করে, সে জীবনে সফল হয়।
* যখন বিপদ আসে, তখন বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।
* যদিও সে গরিব, তবুও সে সৎ।
৩. যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যখন সংযোজক অব্যয় (যেমন: 'এবং', 'ও', 'আর', 'অথবা', 'কিংবা', 'কিন্তু', 'তবু', 'সুতরাং', 'অতএব', 'নতুবা' ইত্যাদি) দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এই বাক্যগুলোর প্রতিটি অংশই স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
* উদাহরণ:
* সে গরিব, কিন্তু সৎ।
* আমি বাড়ি যাব, এবং সেখানে পড়াশোনা করব।
* সে অসুস্থ, সুতরাং আজ স্কুলে আসবে না।
(খ) নির্দেশ অনুসারে যে-কোনো পাঁচটি বাক্যান্তর কর:
এখানে আপনার নির্দেশ অনুসারে বাক্য রূপান্তরগুলো দেওয়া হলো:
(i) জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক)
* জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয়?
(ii) সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক)
* সর্বদা কী দুঃখ তার মনে!
(iii) তিনি ধনী কিন্তু দাতা নন। (সরল)
* তিনি ধনী হলেও দাতা নন।
(iv) সূর্যোদয়ে পদ্ম ফুটে। (জটিল)
* যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পদ্ম ফোটে।
(v) তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। (অস্তিবাচক)
* তাদের ভুলটা দ্রুত ভাঙে।
(vi) কী ভয়ংকর ঘটনা! (নির্দেশাত্মক)
* ঘটনাটি খুব ভয়ংকর।
(vii) মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)
* মানুষ অমরণশীল নয়। (বা, মানুষ অমর নয়।)
(viii) জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন। (যৌগিক)
* তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং তাই বিনয়ী ছিলেন।
(৬)
(ক) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ সংশোধন কর:
অশুদ্ধ অনুচ্ছেদ: নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভুতির কান দ্বারা সে গান শুনিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জিবনের মানে বৃদ্ধি, ধম্মের মানে ও তাই।
শুদ্ধ অনুচ্ছেদ:
নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।
(খ) যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
এখানে প্রদত্ত বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ নিচে দেওয়া হলো:
(i) আমিনা বুদ্ধিমান মেয়ে।
* আমিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
(ii) সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে।
* সব ছাত্র উপস্থিত আছে। (বা, সকল ছাত্র উপস্থিত আছে।)
(iii) তিনি স্বপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত।
* তিনি সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত।
(iv) সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।
* সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
(v) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।
* অশ্রুতে বুক ভেসে গেল। (বা, অশ্রুজলে বাক্যটি প্রচলিত হলেও 'অশ্রু' মানেই জল, তাই 'অশ্রুতে' অধিক শুদ্ধ।)
(vi) পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।
* পরে আপনি আবার আসবেন। (বা, পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন - এটি এখন প্রচলিত, তবে প্রথমটি অধিক শুদ্ধ।)
(vii) মাদকাশক্তি ভালো নয়।
* মাদকাসক্তি ভালো নয়।
(viii) সাবধান পূর্বক চলবে।
- সাবধানে চলবে। (বা, সাবধানতার সাথে চলবে।)
(৭)
(ক) যে কোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:
এখানে প্রদত্ত শব্দগুলোর পারিভাষিক রূপ দেওয়া হলো:
-
Republic: প্রজাতন্ত্র
-
Eye-wash: লোকদেখানো/চোখে ধুলো
-
Ethics: নীতিশাস্ত্র/নীতিবিদ্যা
-
Global: বৈশ্বিক
-
Home Ministry: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
-
File: নথি
-
Legend: কিংবদন্তি
-
National Assembly: জাতীয় সংসদ
-
Organization: সংস্থা
-
Passport: ছাড়পত্র/পাসপোর্ট
-
Pension: অবসরভাতা
-
Range: সীমা/পাল্লা
-
Symbol: প্রতীক
-
Sanction: অনুমোদন/মঞ্জুরি/নিষেধাজ্ঞা
-
Workshop: কর্মশালা
(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
ইংরেজি অনুচ্ছেদ: Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.
বাংলা অনুবাদ:
বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এই দেশের নীল আকাশ আর নির্মল বাতাস আমাদের কাছে খুব প্রিয়। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। যদি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি, তবেই আমাদের দেশের উন্নতি হবে।
(৮)
(ক) যে কোনো ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ঘটনা নিয়ে দিনলিপি রচনা কর।
দিনলিপি: মহাস্থানগড় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫
সময়: রাত ১০:০০টা
আজকের দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলেজের বার্ষিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে আমরা বগুড়ার ঐতিহাসিক মহাস্থানগড় ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সকাল ৭টায় আমাদের বাস কলেজের গেট থেকে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ যাত্রাপথে বন্ধুদের সাথে গান আর আড্ডায় সময়টা ভালোই কাটছিল।
বেলা ১১টা নাগাদ আমরা মহাস্থানগড়ে পৌঁছাই। বাস থেকে নেমেই যেন ইতিহাসের এক প্রাচীন পাতায় পা রাখলাম। চারদিকে কেবল প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ছড়াছড়ি। প্রথমেই আমরা জাদুঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের মুদ্রা, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি এবং অন্যান্য প্রত্নবস্তু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শিক্ষক আমাদের প্রতিটি জিনিসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন, যা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার বছর আগের সভ্যতা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
এরপর আমরা মূল প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাগুলো ঘুরে দেখলাম। গোকুল মেধ (বেহুলার বাসরঘর), মহাস্থানগড় দুর্গ, শুঁড়ঙ্গ পথ, কালীদহের ঘাট—প্রতিটি স্থানই যেন নিজস্ব গল্প বলছিল। বিশেষ করে দুর্গপ্রাচীর এবং এর বিশালতা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম এই স্থানে কীভাবে একসময় সমৃদ্ধ এক জনপদ গড়ে উঠেছিল, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। সেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
বিকেলের দিকে সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, তখন মহাস্থানগড়ের পরিবেশে এক অদ্ভুত মায়াময়তা নেমে আসে। সেই দৃশ্য চিরকাল আমার মনে গেঁথে থাকবে। ইতিহাসের পাতায় পড়া বিষয়গুলো যখন বাস্তবতার সাথে মিশে যায়, তখন তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। এই ভ্রমণ কেবল বিনোদনমূলক ছিল না, এটি আমার ঐতিহাসিক জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। নতুন কিছু শেখার এবং প্রাচীন সভ্যতার সাথে পরিচিত হওয়ার এক অসাধারণ সুযোগ ছিল এটি। রাত ৮টায় ফিরে এলাম, কিন্তু মহাস্থানগড়ের স্মৃতি আজও আমার মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে।
(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
প্রতিবেদন
শিরোনাম: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি: জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব
প্রতিবেদকের নাম: [আপনার নাম/ক, খ, গ]
তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫
স্থান: চট্টগ্রাম
ভূমিকা:
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এক চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, পেঁয়াজ, সবজি থেকে শুরু করে প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই মূল্যবৃদ্ধি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
মূল্যবৃদ্ধির কারণসমূহ:
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করা যায়:
১. সরবরাহ সংকট ও সিন্ডিকেট: অনেক সময় কৃত্রিমভাবে সরবরাহ সংকট তৈরি করে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও বাজারে কৃত্রিম সংকট দেখানো হয়।
২. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি: কৃষি উৎপাদন ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি (যেমন: সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি) পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।
৩. পরিবহন খরচ বৃদ্ধি: জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় পণ্যের খুচরা মূল্যও বৃদ্ধি পায়।
৪. আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব: বিশ্ববাজারে কাঁচামাল বা আমদানি নির্ভর পণ্যের দাম বাড়লে তার প্রভাব দেশীয় বাজারেও পড়ে।
৫. বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ: অতিবৃষ্টি, বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হলে বা উৎপাদন ব্যাহত হলে বাজারে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে।
৬. নিয়ম-নীতির দুর্বলতা ও তদারকির অভাব: সরকারের পক্ষ থেকে বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজির সুযোগ করে দেয়।
৭. মুদ্রাস্ফীতি: টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াও মূল্যবৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।
জনজীবনে প্রভাব:
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে:
-
খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত: নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার কেনা কঠিন হয়ে পড়েছে, যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে।
-
স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি: পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা।
-
শিক্ষা ও অন্যান্য খাতে প্রভাব: নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে বেশি খরচ করতে গিয়ে মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।
-
অর্থনৈতিক চাপ: সীমিত আয়ের মানুষের উপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, ফলে তাদের সঞ্চয় কমে যাচ্ছে এবং অনেকেই ঋণগ্রস্ত হচ্ছে।
-
সামাজিক অস্থিরতা: দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবৃদ্ধি সমাজে অসন্তোষ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
প্রতিকার ও সুপারিশ:
এই সমস্যা মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:
-
বাজার তদারকি জোরদার: নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
-
সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।
-
কৃষি খাতে ভর্তুকি: কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমাতে সার, বীজ ও বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি অব্যাহত রাখা।
-
জ্বালানি তেলের মূল্য স্থিতিশীল রাখা: পরিবহন খরচ নিয়ন্ত্রণে জ্বালানি তেলের দাম স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা।
-
জনসচেতনতা বৃদ্ধি: সিন্ডিকেট ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা।
উপসংহার:
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি জাতীয় সমস্যা, যা সমাধানের জন্য সরকার, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাসমাজ – সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে স্বস্তিদায়ক করা সম্ভব।
(৯)
(ক) মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুকে একটি ই-মেইল প্রেরণ কর।
বিষয়: মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে কিছু জরুরি কথা
প্রিয় [বন্ধুর নাম],
কেমন আছিস? আশা করি ভালো আছিস। আজ তোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার জন্য ইমেইল করছি, যেটা আজকাল আমাদের সবার জন্যই খুব প্রাসঙ্গিক। সেটা হলো মোবাইল ফোনের অপব্যবহার এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো।
আমরা জানি, মোবাইল ফোন যোগাযোগ এবং তথ্য পাওয়ার জন্য দারুণ একটি সহায়ক যন্ত্র। কিন্তু ইদানীং এর অপব্যবহার এতটাই বেড়েছে যে, মনে হয় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছে।
প্রথমত, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। একটানা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকায় চোখ ব্যথা হয়, ঘুম কমে যায়, এবং মানসিক চাপ বাড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটানোয় পড়াশোনা বা কাজের মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, এটি সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করছে। দেখবি, এখন আমরা সামনাসামনি বসেও একজন আরেকজনের সাথে কথা না বলে ফোনে ব্যস্ত থাকি। এতে পারিবারিক বন্ধন ও বন্ধুদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।
তৃতীয়ত, মোবাইলের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ ও ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে। ফিশিং, হ্যাকিং, বা গুজব ছড়ানোর মতো ঘটনা ঘটছে, যা আমাদের নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তি নষ্ট করে।
সবচেয়ে বড় কথা, এটি আমাদের সময় এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে। পরীক্ষার আগে দেখবি, বন্ধুদের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বা গেমে এত বেশি সময় নষ্ট করে যে, পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না।
আমার মনে হয়, আমাদের সবারই মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া দরকার। নিজের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেওয়া ভালো, যখন ফোন ব্যবহার করব না। পড়াশোনার সময় ফোন দূরে রাখা, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলোর নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা - এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলোই অনেক কাজে দেবে।
তুই কী ভাবছিস এই ব্যাপারে? তোর মতামত জানাস।
ভালো থাকিস।
শুভেচ্ছান্তে,
[তোমার নাম]
[তোমার ইমেইল ঠিকানা]
(খ) সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
তারিখ: ২৯ জুন, ২০২৫
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক/সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
[বিদ্যালয়ের নাম]
[বিদ্যালয়ের ঠিকানা, যেমন: চট্টগ্রাম]
বিষয়: সহকারী শিক্ষক (বাংলা/ইংরেজি/গণিত - আপনার বিষয় উল্লেখ করুন) পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।
মহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত [তারিখ] তারিখে [সংবাদপত্র/ওয়েবসাইট-এর নাম] পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা/ইংরেজি/গণিত) পদের শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সূত্র ধরে আমি উক্ত পদে আমার প্রার্থীতা পেশ করছি। আমি উক্ত পদের জন্য একজন আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চাই।
আমি [আপনার নাম]। আমি [বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের নাম] থেকে [আপনার বিষয়] বিষয়ে [স্নাতক/স্নাতকোত্তর] ডিগ্রি অর্জন করেছি। [যদি থাকে: আমি [প্রতিষ্ঠানের নাম] থেকে [বিষয়] বিষয়ে [ডিগ্রি/ডিপ্লোমা] সম্পন্ন করেছি।] শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি এই আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।
আমি মনে করি, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা (যদি থাকে) এবং শিক্ষকতার প্রতি গভীর আগ্রহ আমাকে এই পদের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে। আমি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করতে এবং তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত আগ্রহী। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এই বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে আমি সাধ্যমতো অবদান রাখতে পারব।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর সদয় বিবেচনাপূর্বক আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দানে বাধিত করবেন।
বিনীত নিবেদক,
[আপনার পূর্ণ নাম]
পিতা: [পিতার নাম]
মাতা: [মাতার নাম]
স্থায়ী ঠিকানা: [গ্রাম/মহল্লা], [উপজেলা/থানা], [জেলা]
যোগাযোগের নম্বর: [আপনার ফোন নম্বর]
ই-মেইল: [আপনার ই-মেইল ঠিকানা]
সংযুক্তি:
-
পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (CV)
-
সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি
-
জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি
-
চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি
-
পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (২ কপি)
(১০)
(ক) সারাংশ লেখ:
মূল অনুচ্ছেদ:
স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন হয়, তেমনই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।
সারাংশ:
স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা অপরিহার্য। মিথ্যাচারী জাতি কখনোই উন্নতির মুখ দেখে না। যে সমাজে মিথ্যাচার প্রবল, সেখানে সত্যবাদীদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবে, জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইলে এই কষ্ট স্বীকার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা অপরিহার্য।
(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর: তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?
ভাব-সম্প্রসারণ:
"তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" - এই উক্তিটি মানবীয় আচরণ ও নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এর মূল অর্থ হলো, কেউ যদি নিম্নমানের বা মন্দ আচরণ করে, তার মানে এই নয় যে আমাকেও তার মতো অধম হতে হবে। বরং, এমন পরিস্থিতিতে আমার উচিত নিজের উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আদর্শ বজায় রাখা।
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে, যাদের আচরণ ও চিন্তাভাবনা ভিন্ন হয়। কিছু মানুষ সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ বা অসৎ হতে পারে। তাদের মন্দ আচরণ দেখে আমাদের মনে প্রতিশোধপরায়ণতা বা ঘৃণা জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই উক্তিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অন্যের মন্দ কাজ দেখে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি অমানবীয় আচরণ করে, তার প্রত্যুত্তরে যদি আমরাও একই ধরনের আচরণ করি, তাহলে আমাদের নিজেদের নৈতিক মান নেমে যায়। এতে সমাজের সামগ্রিক অধঃপতন ঘটে।
উত্তম চরিত্র এবং সুব্যবহার কেবল ব্যক্তিগত গুণই নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব। আমাদের উচিত নিজেদের নৈতিক আদর্শে অটল থাকা, অন্যের মন্দ আচরণকে নিজেদের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ না করা। বরং, নিজের সততা, উদারতা ও সহনশীলতা দিয়ে অন্যের মন্দতাকে পরাজিত করার চেষ্টা করাই প্রকৃত মহত্ত্ব। এর মাধ্যমে আমরা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি এবং নিজেকে একজন উন্নত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এই নীতি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই উন্নত করার প্রেরণা যোগায়। কারণ, একজন আদর্শবান ব্যক্তি তাঁর চারপাশের পরিবেশকেও প্রভাবিত করতে পারেন এবং মন্দকে ভালোতে রূপান্তরিত করার শক্তি রাখেন।
(১১)
(ক) লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
সংলাপ: লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ভাবনা
অমিত: কিরে রাহুল, আজকাল দেখি তোর হাতে সবসময় বই থাকে? কী ব্যাপার, হঠাৎ এত বইপ্রেমী হয়ে গেলি?
রাহুল: হ্যাঁ রে অমিত, আজকাল বইয়ের জগতে ডুবে আছি। যত পড়ছি, তত বুঝতে পারছি আমাদের এলাকায় একটা ভালো লাইব্রেরির কত প্রয়োজন!
অমিত: লাইব্রেরি? সেটা আবার কেন? এখন তো সবই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।
রাহুল: সব কিছু ইন্টারনেটে পাওয়া গেলেও বই পড়ার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু অন্যরকম। আর সবার পক্ষে তো সব বই কিনে পড়া সম্ভব নয়, তাই না? একটা লাইব্রেরি থাকলে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে গরিব শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বা কম খরচে বই পড়ার সুযোগ পাবে।
অমিত: হুম, কথাটা মন্দ বলিসনি। আমাদের এলাকায় তো একটাও ভালো লাইব্রেরি নেই। লাইব্রেরি থাকলে ছেলেমেয়েরা স্মার্টফোন আর গেমের পেছনে সময় নষ্ট না করে বই পড়তে উৎসাহিত হবে। তাতে পড়ার অভ্যাসও গড়ে উঠবে।
রাহুল: ঠিক তাই। লাইব্রেরি শুধু বই পড়ার জায়গাই নয়, এটা একটা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানে মানুষ এসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে, নতুন কিছু শিখতে পারবে। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও রাখা যেতে পারে, যাতে সবাই সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান রাখতে পারে।
অমিত: কিন্তু একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা তো সহজ কাজ নয়। অনেক টাকা লাগবে, জায়গার প্রয়োজন হবে।
রাহুল: জানি, কাজটা কঠিন। তবে আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো সম্ভব। প্রথমে আমাদের একটা কমিটি গঠন করা উচিত। তারপর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি এবং বইপ্রেমীদের সাথে আলোচনা করতে পারি। একটা ছোট পরিসরে শুরু করা যেতে পারে, তারপর ধীরে ধীরে বড় করা যাবে।
অমিত: আইডিয়াটা কিন্তু দারুণ! আমি তোর সাথে আছি। চল, আজই কয়েকজন বন্ধুর সাথে বসে একটা প্রাথমিক পরিকল্পনা করি। আমাদের এই স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সমাজের অনেক বড় একটা উপকার হবে।
রাহুল: সেটাই তো! একটা লাইব্রেরি শুধু একটি ভবন নয়, এটা জ্ঞানের আলো ছড়ানোর এক কেন্দ্র। চল, আজ থেকেই শুরু করি।
(খ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর: মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান...
মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান
গ্রামের একমাত্র ভরসা ছিল হাসান। তার বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের অসুস্থ শরীর আর ছোট দুই বোনের দায়িত্ব এসে পড়েছিল কাঁধে। পড়াশোনায় ভালো হলেও, টাকার অভাবে আর এগোতে পারেনি। দিনমজুরি করে যা রোজগার করত, তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলত। মায়ের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়া বা চিকিৎসার জন্য টাকা জমানো তার পক্ষে সম্ভব হতো না। প্রতি রাতে যখন মায়ের কাশি আর ব্যথার শব্দ শুনত, হাসানের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠত। মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতো হাসান, যেন আগুন লেগেছে তার ভেতরে।
একদিন শহরে এক আত্মীয়ের কাছে খবর পেল, সেখানে ভালো বেতনে কাজের সুযোগ আছে। মায়ের অসুস্থতার কথা ভেবে হাসান স্থির করল, তাকে শহরে যেতেই হবে। চোখের জল ফেলে মাকে রেখে সে পাড়ি জমাল শহরের উদ্দেশে। প্রথম কয়েকটা মাস খুব কষ্টে কাটল। দিনের পর দিন না খেয়েও কাজ করে যেত সে। একটাই স্বপ্ন দেখত – একদিন অনেক টাকা রোজগার করে মায়ের উন্নত চিকিৎসা করাবে, বোনদের মুখে হাসি ফোটাবে।
প্রায় দু'বছর পর, যখন হাসান ভালো একটা কাজ জোগাড় করে টাকা পাঠাতে শুরু করল, তখন তার মনে কিছুটা শান্তি এলো। প্রতি মাসেই সে মায়ের জন্য টাকা পাঠাত, খোঁজ নিত। কিন্তু কাজের চাপে আর গ্রামের পথঘাটের জটিলতার কারণে মায়ের কাছে যেতে পারত না।
একদিন মাঝরাতে বোনের ফোন এলো। “ভাইয়া, মা আর নেই!” কথাটা শুনে হাসানের পৃথিবীটা যেন থমকে গেল। ফোনটা হাতে নিয়েই সে বসে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, সে এত কীসের জন্য কষ্ট করল? মায়ের সেবা করবে বলে শহরে এসেছিল, টাকা রোজগার করল, কিন্তু মা চলে গেলেন। মা যে শেষ সময়ে তার পাশে থাকতে চেয়েছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষা সে পূরণ করতে পারল না।
হাসান ছুটে গ্রামে ফিরে এলো, কিন্তু মায়ের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, তার সমস্ত অর্জন বৃথা। মায়ের শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় সে পাশে ছিল না। আজ তার কাছে টাকা আছে, কিন্তু তার মা নেই। সেইদিন থেকে মাকে সেবা করতে না পারার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় হাসান। এই যন্ত্রণা তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়াবে, এক অমলিন ক্ষত হয়ে বুকে বিঁধে থাকবে।
(১২)
আপনার পছন্দ অনুযায়ী আমি 'শিষ্টাচারের গুরুত্ব' বিষয়টি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করছি।
(ক) শিষ্টাচারের গুরুত্ব
ভূমিকা:
মানব সমাজে শিষ্টাচার একটি অপরিহার্য গুণ, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। শিষ্টাচার বলতে বোঝায় সুন্দর, মার্জিত ও বিনয়ী আচরণ, যা অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটায়। সভ্য সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কেবল ব্যক্তির চরিত্রকেই উন্নত করে না, বরং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সুদৃঢ় করে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে।
শিষ্টাচার কী?
শিষ্টাচার হলো সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতির সমষ্টি, যা মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরা, কথা বলা, মেলামেশা এবং সামগ্রিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভালো অভ্যাস ও নৈতিকতার প্রতিফলন। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, সহকর্মীদের প্রতি সহযোগিতা, এবং অপরিচিতদের প্রতি ভদ্রতা - এ সবকিছুই শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। সালাম বিনিময়, কুশল জিজ্ঞাসা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ক্ষমা চাওয়া, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি শিষ্টাচারেরই অংশ।
ব্যক্তিগত জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব:
ব্যক্তিগত জীবনে শিষ্টাচার মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। একজন শিষ্ট ব্যক্তি সর্বদা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হন। তার আচরণে বিনয়, ভদ্রতা ও নম্রতা প্রকাশ পায়, যা তাকে সকলের কাছে প্রিয় করে তোলে। শিষ্টাচার মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তার ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এটি মানুষকে ধৈর্যশীল, সহনশীল ও সংযমী হতে শেখায়, যা ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। একজন শিষ্ট ব্যক্তি সহজেই অন্যের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকতে পারেন।
সামাজিক জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব:
সামাজিক জীবনে শিষ্টাচার সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিষ্টাচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা, ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, এবং বৃহত্তর সমাজে শিষ্টাচার বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
-
পারিবারিক সম্পর্ক: শিষ্টাচার পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শিষ্টাচারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।
-
কর্মক্ষেত্র: পেশাগত জীবনে শিষ্টাচার মানুষকে সফল হতে সাহায্য করে। সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং একটি ইতিবাচক কর্মপরিবেশ তৈরিতে এটি অপরিহার্য।
-
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিষ্টাচার গড়ে তোলা হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রশস্ত করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক শিষ্টাচারের উপর নির্ভরশীল।
-
সামাজিক সম্প্রীতি: শিষ্টাচার ভিন্ন মত ও পথের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ায়, যা সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করে।
ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিষ্টাচার:
প্রায় সব ধর্মেই শিষ্টাচার ও সদ্গুণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকল ধর্মেই মানুষকে বিনয়ী, ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিষ্টাচার নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং মানুষকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে উৎসাহিত করে।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিষ্টাচারের গুরুত্ব:
আধুনিক যুগে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগে এক ধরনের যান্ত্রিকতা এসেছে। ফলে অনেক সময় শিষ্টাচারের চর্চা কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিষ্টাচারের গুরুত্ব আরও বেশি। অনলাইনেও ভদ্র ও দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখা (Netiquette) বর্তমান সময়ে অত্যন্ত জরুরি।
উপসংহার:
শিষ্টাচার একটি উন্নত ও সভ্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। এটি এমন এক গুণ যা মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে এবং তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচিত করে তোলে। শিষ্টাচারের চর্চা ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন সুন্দর করে তোলে, তেমনি সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত ছোটবেলা থেকেই শিষ্টাচারের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঠিক চর্চা করা। শিষ্টাচার বজায় রাখলে মানবসমাজ আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।