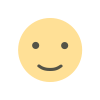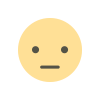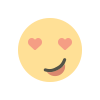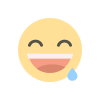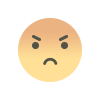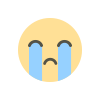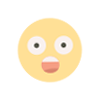এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। বরিশাল বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। বরিশাল বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
১. (ক) ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:
ম-ফলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যা বাংলা শব্দকে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে সাহায্য করে। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ দেওয়া হলো:
১. শব্দের আদিতে ম-ফলা: শব্দের শুরুতে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ সাধারণত অনুচ্চারিত থাকে এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে সামান্য নাসিক্য হয়।
* উদাহরণ: স্মরণ (উচ্চারণ: শোরোন), স্মৃতি (উচ্চারণ: শ্রি-তি)।
২. শব্দের মাঝে বা শেষে ম-ফলা: শব্দের মাঝখানে বা শেষে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ প্রায়শই বজায় থাকে এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে।
* উদাহরণ: পদ্ম (উচ্চারণ: পোদ্-দো), আত্মা (উচ্চারণ: আত্-তা)।
৩. গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল, শ, ষ, স - এই বর্ণগুলোর সাথে ম-ফলা: এই বর্ণগুলোর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-এর উচ্চারণ অনেকটা অনুচ্চারিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বর্ণের উচ্চারণ নাসিক্য হয়।
* উদাহরণ: বাগ্মী (উচ্চারণ: বাগ্-মি), যুগ্ম (উচ্চারণ: জুগ-মো)।
৪. যুক্তব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা: যদি কোনো যুক্তব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা যুক্ত হয়, তবে ম-এর উচ্চারণ প্রায়শই অনুচ্চারিত থাকে এবং যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের ওপর জোর পড়ে।
* উদাহরণ: লক্ষ্মণ (উচ্চারণ: লক-খোঁন), ভস্ম (উচ্চারণ: ভশ-মো)।
৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে: অনেক সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে ম-ফলা তার নিজস্ব উচ্চারণ বজায় রাখে, বিশেষ করে যখন এটি একটি শব্দের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
* উদাহরণ: শ্মশান (উচ্চারণ: শ্মো-শান), ব্রহ্মা (উচ্চারণ: ব্রোম-হা)।
১. (খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ:
-
অধ্যক্ষ: ওদ্ধোক্খো
-
একটি: অ্যাঁকটি
-
গণিত: গঁনিত
-
চলন্ত: চলোন্তো
-
নদী: নোদি
-
বিদ্বান: বিদ্দান্
-
লাবণ্য: লাবোন্নো
-
লক্ষ্মণ: লক-খোঁন
২. (ক) বাংলা বানানে ই-কার (ি) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:
বাংলা বানানে ই-কার (ি) ব্যবহারের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যা সঠিক বানান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ দেওয়া হলো:
১. তৎসম শব্দে ই-কার: অধিকাংশ তৎসম (সংস্কৃত থেকে আগত) শব্দে 'ই' বা 'ঈ' ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত রূপটি অনুসরণ করা হয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি আধুনিকীকরণের জন্য কিছু তৎসম শব্দেও ই-কার ব্যবহারের নিয়ম করেছে।
* উদাহরণ: সরকারি (সরকার + ই), শ্রেণি (আগে 'শ্রেণী' লেখা হতো), ধ্বনি (আগে 'ধ্বনিত' লেখা হতো)।
২. বিদেশি শব্দে ই-কার: সকল প্রকার বিদেশি (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দে কেবল ই-কার (ি) ব্যবহৃত হয়। এই নিয়মটি বাংলা বানানে সরলতা এনেছে।
* উদাহরণ: স্টিমার, নভেম্বর, ফ্রেন্ডশিপ, জানুয়ারি, ফুটবল, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি।
৩. অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে: তৎসম নয় এমন সব শব্দে (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র) সর্বদা ই-কার (ি) ব্যবহার করা হয়।
* উদাহরণ: বাঙালি, কুমির, চিরুনি, শাড়ি।
৪. স্ত্রীবাচক শব্দে ই-কার: যদি স্ত্রীবাচক কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহলে ই-কার ব্যবহার করা হয়।
* উদাহরণ: শিক্ষিকা, লেখিকা, ছাত্রী।
৫. বিশেষণ পদ গঠনে ই-কার: অনেক সময় বিশেষ্য পদ থেকে বিশেষণ পদ গঠন করার সময় ই-কার ব্যবহার করা হয়।
* উদাহরণ: জাতি থেকে জাতীয়, পরিবার থেকে পারিবারিক।
২. (খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান:
-
বাঙালি (বাংগালী)
-
শাশ্বত (শ্বাশত)
-
দৈন্য (দৈন্যতা)
-
সন্ন্যাসী (সন্যাসী)
-
পুরস্কার (পুরষ্কার)
-
মুহূর্ত (মুহুর্ত)
-
ঐকতান (ঐক্যতান)
-
বুদ্ধিজীবী (বুদ্ধিজিবি)
৩. (ক) উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা:
ক্রিয়াপদ হলো সেই পদ যা দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া বা ঘটা বোঝায়। বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে সাধারণত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে প্রধান কিছু শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং বাক্যটি শেষ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: ছেলেটি খেলছে। (এখানে 'খেলছে' ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে।)
২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না এবং বাক্যটি আরও কিছু অংশের উপর নির্ভর করে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে 'ইয়ে', 'লে', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত থাকে।
* উদাহরণ: ছেলেটি খেলে ভাত খাবে। (এখানে 'খেলে' অসমাপিকা ক্রিয়া, যা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করেনি।)
৩. সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, অর্থাৎ যাকে প্রশ্ন করলে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: সে বই পড়ছে। (এখানে 'কী পড়ছে?' - 'বই', তাই 'পড়ছে' সকর্মক ক্রিয়া।)
৪. অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, অর্থাৎ যাকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: সে ঘুমায়। (এখানে 'কী ঘুমায়?' বা 'কাকে ঘুমায়?' - কোনো উত্তর নেই, তাই 'ঘুমায়' অকর্মক ক্রিয়া।)
৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে (একটি মুখ্য কর্ম এবং একটি গৌণ কর্ম), তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়।
* উদাহরণ: বাবা আমাকে কলম দিলেন। (এখানে 'আমাকে' গৌণ কর্ম এবং 'কলম' মুখ্য কর্ম।)
৬. যৌগিক ক্রিয়া: দুটি ক্রিয়াপদ একত্রিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে এটি গঠিত হয়।
* উদাহরণ: সে খেতে শুরু করল। (এখানে 'খেতে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'শুরু করল' সমাপিকা ক্রিয়া মিলে যৌগিক ক্রিয়া।)
৭. প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজটি করায়, তখন তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যে কাজ করায় সে প্রযোজক কর্তা এবং যাকে দিয়ে কাজ করানো হয় সে প্রযোজ্য কর্তা।
* উদাহরণ: মা শিশুকে চাঁদ দেখান। (এখানে মা প্রযোজক কর্তা, শিশু প্রযোজ্য কর্তা এবং 'দেখান' প্রযোজক ক্রিয়া।)
৩. (খ) নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ:
ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে বাক্যের মধ্যে পদের কার্যকারিতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যাস করাকে বোঝায়। নিচে নির্দেশিত শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি দেওয়া হলো:
(i) মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।
* মোদের: সর্বনাম (আমরা শব্দের সম্বন্ধ পদ)
(ii) হে বন্ধু, বিদায়।
* হে: অব্যয় (সম্বোধনবাচক অব্যয়)
(iii) আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর।
* ছোট ছোট: বিশেষণ (ঘরের আকার নির্দেশ করছে, এটি একটি দ্বিরুক্ত শব্দ)
(iv) যথা ধর্ম, তথা জয়।
* যথা: অব্যয় (তুলনাবাচক অব্যয়)
* তথা: অব্যয় (তুলনাবাচক অব্যয়)
(v) এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।
* প্রতিবাদী: বিশেষণ (মিছিলের প্রকৃতি নির্দেশ করছে)
(vi) আমায় যদি কান্দাও বন্ধু, তোমার কান্দন পরে।
* পরে: অব্যয় (স্থানবাচক অব্যয়)
(vii) তুমি যে আমার কবিতা।
* তুমি: সর্বনাম
(viii) প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।
* প্রগাঢ়: বিশেষণ (নিকুঞ্জের গভীরতা নির্দেশ করছে)
৪. (ক) "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"-আলোচনা কর:
উপসর্গ হলো কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ যা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটায়। "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে" - এই উক্তিটি বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।
অর্থবাচকতা নেই:
উপসর্গের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র কোনো অর্থ নেই। যদি আমরা 'প্র', 'পরা', 'অপ', 'সম', 'নি', 'অব' - এমন কোনো উপসর্গকে এককভাবে ব্যবহার করি, তবে তাদের কোনো সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। যেমন, 'প্র' বললে এর কোনো নির্দিষ্ট মানে বোঝা যায় না, এটি কোনো বস্তু, গুণ বা কাজের নাম নির্দেশ করে না। তাই বলা হয়, উপসর্গের নিজস্ব অর্থবাচকতা নেই।
অর্থদ্যোতকতা আছে:
যদিও উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই, কিন্তু এরা যখন কোনো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে, তখন তারা সেই মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, অর্থের ব্যঞ্জনা বা দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই ক্ষমতাকেই অর্থদ্যোতকতা বলা হয়। অর্থাৎ, উপসর্গ নতুন অর্থের ইঙ্গিত দেয় বা বিদ্যমান অর্থের একটি বিশেষ দিককে উদ্ভাসিত করে।
উদাহরণস্বরূপ:
-
'হার' একটি শব্দ, যার অর্থ পরাজয় বা গলার অলংকার।
-
এর পূর্বে 'প্র' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'প্রহার' (অর্থ: আঘাত করা)। এখানে 'প্র' 'হার' শব্দের অর্থে নতুনত্ব এনেছে।
-
'উপ' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'উপহার' (অর্থ: ভেট, দান)। এখানেও 'উপ' নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।
-
'আ' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'আহার' (অর্থ: খাওয়া)।
-
'বি' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'বিহার' (অর্থ: ভ্রমণ)।
-
'সম' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'সংহার' (অর্থ: বিনাশ)।
-
লক্ষ্য করুন, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'হার' শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থ ধারণ করেছে উপসর্গের প্রভাবে। 'প্র', 'উপ', 'আ', 'বি', 'সম' - এই উপসর্গগুলো নিজস্বভাবে অর্থহীন হলেও, 'হার' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে তার অর্থের দ্যোতনা ঘটিয়েছে।
এইভাবে, উপসর্গগুলো মূল শব্দের অর্থের সাথে মিশে গিয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এটি একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই, এই উক্তিটি উপসর্গের প্রকৃতিকে যথার্থভাবে বর্ণনা করে - তাদের নিজস্ব অর্থ না থাকলেও তারা শব্দের অর্থে পরিবর্তন, বিস্তার বা সংকোচন ঘটিয়ে থাকে।
৪. (খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়:
সমাস হলো দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার প্রক্রিয়া, যার ফলে একটি নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়। নিচে প্রদত্ত শব্দগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করা হলো:
-
আয়ব্যয়:
-
ব্যাসবাক্য: আয় ও ব্যয়
-
সমাস: দ্বন্দ্ব সমাস
-
-
সপ্তর্ষি:
-
ব্যাসবাক্য: সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার
-
সমাস: দ্বিগু সমাস
-
-
রাজনীতি:
-
ব্যাসবাক্য: রাজার নীতি
-
সমাস: ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
-
-
আলুনি:
-
ব্যাসবাক্য: নুন নেই যার (অর্থাৎ লবনহীন)
-
সমাস: নঞ্ বহুব্রীহি সমাস
-
-
বিলাতফেরত:
-
ব্যাসবাক্য: বিলাত হতে ফেরত
-
সমাস: পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
-
-
নদীমাতৃক:
-
ব্যাসবাক্য: নদী মাতা যার
-
সমাস: বহুব্রীহি সমাস
-
-
চিরসুখী:
-
ব্যাসবাক্য: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
-
সমাস: ২য়া তৎপুরুষ সমাস (এখানে 'চিরকাল ব্যাপিয়া' বোঝাতে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়)
-
-
প্রবচন:
-
ব্যাসবাক্য: প্রকৃষ্ট যে বচন
-
সমাস: প্রাদি সমাস (এখানে 'প্র' উপসর্গটি বচন শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে।)
-
৫. (ক) অর্থানুসারে বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও:
অর্থ অনুসারে বাংলা বাক্যকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগগুলো বক্তার মনোভাব বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়। নিচে প্রকারভেদগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. নির্দেশাত্মক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা কোনো তথ্য, ঘটনা বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তাকে নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। এই বাক্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় - হ্যাঁ-সূচক (অস্তিবাচক) ও না-সূচক (নেতিবাচক)।
* উদাহরণ (হ্যাঁ-সূচক): আমি ভাত খাই।
* উদাহরণ (না-সূচক): আমি ভাত খাই না।
২. প্রশ্নবাচক বাক্য (প্রশ্নবোধক বাক্য): যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা প্রশ্ন করা হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে। এই বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) থাকে।
* উদাহরণ: তুমি কি যাচ্ছো?
৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, নিষেধ বা অনুমতি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।
* উদাহরণ: বইটি নিয়ে এসো (আদেশ)। মন দিয়ে পড়ালেখা করো (উপদেশ)। এক গ্লাস জল দাও (অনুরোধ)।
৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা বক্তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আশীর্বাদ বা শুভকামনা প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে।
* উদাহরণ: ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য (আবেগসূচক বাক্য): যে বাক্য দ্বারা বক্তার বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। এই বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) থাকে।
* উদাহরণ: কী সুন্দর দৃশ্য! আহা, কী কষ্ট!
৫. (খ) নির্দেশ অনুসারে যে-কোনো পাঁচটি বাক্যান্তর কর:
বাক্যান্তর বলতে এক প্রকার বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করাকে বোঝায়, যেখানে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। নিচে নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তরিত করা হলো:
(i) লোকটি ধনী, কিন্তু উদার নয়। (জটিল)
* রূপান্তরিত বাক্য: যে লোকটি ধনী, সে উদার নয়।
(ii) এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।
(iii) কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)
* রূপান্তরিত বাক্য: আপনি কিছু বলবেন না। (এখানে 'কিছু বলবেন না' বাক্যটি নিজেই নির্দেশাত্মক, তবে আরও স্পষ্ট করতে 'আপনি' যোগ করা হলো)।
(iv) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: বিপদে অধীর হয়ো না।
(v) তুমি অন্যায় কাজ করেছ। (নেতিবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: তুমি ন্যায় কাজ করোনি।
(vi) যার গুণ আছে, সে বিনয়ী হয়। (সরল)
* রূপান্তরিত বাক্য: গুণী ব্যক্তি বিনয়ী হয়।
(vii) এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধ)
* রূপান্তরিত বাক্য: কী বিচিত্র এ দেশ!
(viii) সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)
* রূপান্তরিত বাক্য: সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ?
৬. (ক) নিচের যে-কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
বাক্য শুদ্ধিকরণ হলো ব্যাকরণগত ত্রুটি, বানান ভুল বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার পরিহার করে একটি বাক্যের সঠিক ও সুন্দর রূপ দেওয়া। নিচে প্রদত্ত বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো:
(i) তিনি সপরিবারে ঢাকা থাকেন। (স্বপরিবারে-এর বদলে সপরিবারে হবে)
(ii) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। (প্রতিযোগীতায়-এর বদলে প্রতিযোগিতায় হবে)
(iii) তিনি মামলায় সাক্ষী দেবেন। (মোকদ্দমায়-এর বদলে মামলায় হবে, কারণ 'মোকদ্দমা' একটি ফারসি শব্দ যা 'মামলা' শব্দের সমার্থক এবং বাংলায় 'মামলা' বেশি প্রচলিত।)
(iv) বাজারে গরুর খাঁটি দুধ দুর্লভ। (খাঁটি গরুর দুধ-এর বদলে গরুর খাঁটি দুধ হবে, কারণ দুধ খাঁটি হয়, গরু নয়।)
(v) ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। (ভয়ানক-এর বদলে অত্যন্ত হবে, কারণ 'ভয়ানক' সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।)
(vi) কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন। (কীতিবাস-এর বদলে কৃত্তিবাস এবং রামায়ন-এর বদলে রামায়ণ হবে)
(vii) সব লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল। (সকল লোকেরাই-এর বদলে সব লোকেরাই বা শুধু সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল হবে, কারণ 'সকল' এবং 'লোক' উভয়ই বহুবচন এবং 'সকল লোক' বললে 'সব লোক' বোঝায়। 'সকল লোকেরাই' দ্বিরুক্ত বহুবচন নির্দেশ করে।)
(viii) দৈন্য প্রশংসনীয় নয়। (দৈন্যতা-এর বদলে দৈন্য হবে, কারণ 'দৈন্যতা' একটি ভুল প্রয়োগ, 'দৈন্য' নিজেই একটি বিশেষ্য পদ।)
৬. (খ) অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:
অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভুল বানান, ব্যাকরণগত ত্রুটি এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ করে নিচে লেখা হলো:
আজকাল বানানের ব্যাপারে সব ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা তো সচেষ্ট নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
বিশ্লেষণ ও শুদ্ধিকরণ:
-
আজিকাল আজকাল: সঠিক বানান।
-
সকল ছাত্ররাই সব ছাত্রই: 'সকল' এবং 'ছাত্ররাই' একসাথে দ্বিরুক্তি বা বাহুল্য দোষ তৈরি করেছে। 'সব ছাত্রই' বা 'সকল ছাত্র' হতে পারে। এখানে 'সব ছাত্রই' বেশি শ্রুতিমধুর।
-
তাহারা তারা: আধুনিক চলিত বাংলায় 'তাহারা' না হয়ে 'তারা' ব্যবহৃত হয়।
-
নহেই নয়ই: ক্রিয়াপদের ভুল ব্যবহার। 'নয়ই' সঠিক।
-
অবস্থাদৃষ্টে অবস্থা দেখে: 'অবস্থাদৃষ্টে' একটি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দ, যা এই সরল চলিত অনুচ্ছেদে বেমানান। 'অবস্থা দেখে' বা 'পরিস্থিতি দেখে' অধিক চলিত ও উপযুক্ত।
৭. (ক) যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ:
পারিভাষিক শব্দ হলো এমন বিশেষায়িত শব্দ যা কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখা, পেশা বা কারিগরি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। নিচে দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ দেওয়া হলো:
-
Attestation: সত্যায়ন
-
Bidder: দরদাতা
-
Copyright: স্বত্বাধিকার
-
Dialect: উপভাষা
-
Equation: সমীকরণ
-
Fiction: কথাসাহিত্য / কল্পকাহিনী
-
Gratuity: বকশিশ / অনুতোষিক
-
Hygiene: স্বাস্থ্যবিধি
-
Leap year: অধিবর্ষ
-
Manifesto: ইশতেহার
-
Plosive: স্পর্শধ্বনি
-
X-ray: রঞ্জনরশ্মি
-
Ratio: অনুপাত
-
Specialist: বিশেষজ্ঞ
-
Walk-out: ধর্মঘট / বর্জন
৭. (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some others may give you much pleasure.
অনুবাদ:
বই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। আপনার খুব ভালো বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু যখন তাদের প্রয়োজন হবে, তখন হয়তো তাদের পাবেন না। তারা আপনার সাথে নরম সুরে কথা নাও বলতে পারে। এক বা দুজন হয়তো মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হতে পারে এবং আপনার অনেক ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সবসময় আপনার পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত। কিছু বই আপনাকে হাসাতে পারে। অন্য কিছু বই আপনাকে অনেক আনন্দ দিতে পারে।
৯. (ক) কলেজে প্রথম দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি রচনা:
১৪ই জুন, ২০২৫, শুক্রবার
রাত ৯:০০টা
আজ আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো—কলেজের প্রথম দিন। সকাল থেকেই একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে এক নতুন পরিবেশে পা রাখা, নতুন মানুষজনের সাথে পরিচিত হওয়া—ভাবতেই অন্যরকম লাগছিল।
সকালে মা টিফিন বানিয়ে দিলেন আর বাবা কলেজ গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। গেটে ঢোকার পরই এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। বিশাল ক্যাম্পাস, সারি সারি ভবন আর অসংখ্য অচেনা মুখ। মনে হলো যেন এক বিশাল সমুদ্রে এসে পড়েছি। প্রথমেই বন্ধুদের সাথে ক্লাসরুম খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হলো।
আমাদের প্রথম ক্লাস ছিল বাংলা। শিক্ষক ছিলেন খুবই অমায়িক। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং সবাইকে নিজেদের সম্পর্কে বলতে বললেন। একে একে সবাই নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিল, আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এরা কেমন হবে? বন্ধু হবে তো? ক্লাস শেষে করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, অনেকেই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে।
ক্যান্টিনে গিয়ে দেখলাম উপচে পড়া ভিড়। সেখানে নতুন করে কিছু বন্ধুর সাথে পরিচয় হলো। তারা বেশ হাসিখুশি আর মিশুক। তাদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে কেমন যেন হালকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই নতুন পরিবেশটা হয়তো ততটাও কঠিন হবে না। দুপুরে লাঞ্চের পর লাইব্রেরিটা ঘুরে দেখলাম। অনেক বই আর সাজানো ডেস্ক দেখে মনটা ভরে গেল। ভবিষ্যতে এখানে অনেক সময় কাটানোর পরিকল্পনা করে ফেললাম।
দিনের শেষে কলেজ থেকে ফেরার পথে নিজেকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল। প্রথম দিনের জড়তা অনেকটাই কেটে গেছে। মনে হচ্ছে, এই কলেজ জীবনটা দারুণ হতে চলেছে। নতুন বন্ধু, নতুন শিক্ষক, নতুন পাঠক্রম—সবকিছুই এক নতুন অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই দিনের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে থাকবে।
৯. (খ) 'খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও এর প্রতিকার' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন রচনা:
প্রতিবেদন
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো ও এর প্রতিকার
তারিখ: ২৯শে জুন, ২০২৫
স্থান: চট্টগ্রাম
ভূমিকা:
বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুতর সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা হলো খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো। অসাধু ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে প্রতিনিয়ত খাদ্যপণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এটি কেবল জনস্বাস্থ্যের জন্যই হুমকি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে জাতির ভবিষ্যতের জন্যও একটি অশনি সংকেত।
ভেজাল মেশানোর কারণ:
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর প্রধান কারণগুলো হলো:
-
অতিরিক্ত মুনাফার লোভ: কম দামে ভেজাল মিশিয়ে বেশি দামে বিক্রি করে দ্রুত অর্থ উপার্জনের প্রবণতা।
-
আইনের দুর্বল প্রয়োগ: ভেজালবিরোধী আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা।
-
জনসচেতনতার অভাব: অনেক সময় ক্রেতারা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে না বা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন থাকে না।
-
প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা: ভেজাল শনাক্তকরণের জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরির অপর্যাপ্ততা।
-
কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি: অনেক সময় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ভেজাল পণ্য বেশি দামে বিক্রি করা হয়।
ভেজাল মেশানোর পদ্ধতি ও ব্যবহৃত ক্ষতিকর উপাদান:
বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন উপায়ে ভেজাল মেশানো হয়:
-
ফল ও সবজি: কার্বাইড দিয়ে ফল পাকানো, ফরমালিন দিয়ে টাটকা রাখা।
-
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: পাউডার দুধ, ডিটারজেন্ট, ফরমালিন ও পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি।
-
মাছ: ফরমালিন ব্যবহার করে টাটকা রাখা।
-
মিষ্টি: কাপড় কাচার সোডা, বিষাক্ত রং, কৃত্রিম মিষ্টি ব্যবহার।
-
মশলা: ইটের গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, ধানের তুষ মেশানো।
-
চাল ও ডাল: পাথরকুচি ও কৃত্রিম রং মেশানো।
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা:
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল রোধে নিম্নলিখিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা জরুরি:
-
আইনের কঠোর প্রয়োগ: ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
-
নিয়মিত বাজার তদারকি: খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের প্রতিটি স্তরে সরকারি নজরদারি বৃদ্ধি করা। মোবাইল কোর্টের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা।
-
জনসচেতনতা বৃদ্ধি: গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে ভেজাল পণ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং ভেজাল পণ্য চেনার উপায় সম্পর্কে শিক্ষিত করা।
-
আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন: প্রতিটি জেলায় আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করে দ্রুত খাদ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা।
-
উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ: খাদ্যদ্রব্যের সঠিক উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
-
প্রযুক্তি ব্যবহার: ভেজাল শনাক্তকরণের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
-
সামাজিক আন্দোলন: ভেজালের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
উপসংহার:
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল একটি জাতীয় সমস্যা। এর সমাধান শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সরকার, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, এবং সুশীল সমাজ—সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পারে এই ভয়াবহ ব্যাধি থেকে জাতিকে রক্ষা করতে এবং একটি সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।
৯. (ক) জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল:
বিষয়: জরুরি রক্তের প্রয়োজন - তোমার সাহায্য চাই
প্রিয় [বন্ধুর নাম],
আশা করি ভালো আছিস। তোর কাছে একটা জরুরি প্রয়োজনে লিখছি। আমার ছোট ভাই [ভাইয়ের নাম/যাঁর জন্য রক্ত প্রয়োজন, তাঁর নাম] হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ডাক্তার জানিয়েছেন, তার এখনই [রক্তের গ্রুপ, যেমন: B+ve] রক্তের প্রয়োজন। পরিস্থিতি বেশ গুরুতর।
আমরা রক্তদাতার খোঁজে আছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানি তুই রক্তদানে আগ্রহী এবং তোর রক্তের গ্রুপও [রক্তের গ্রুপ, যেমন: B+ve]। যদি তোর পক্ষে সম্ভব হয়, তবে দয়া করে একটু যোগাযোগ করিস। ডাক্তার বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব রক্তের ব্যবস্থা করা গেলে খুব ভালো হয়।
হাসপাতালের ঠিকানা: [হাসপাতালের নাম ও ঠিকানা]। তুই যখনই আসতে পারিস, আমাকে একটা ফোন দিস। প্রয়োজনে আমি হাসপাতাল থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।
তোর সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দিস।
শুভেচ্ছান্তে,
[তোমার নাম]
[তোমার ফোন নম্বর]
[তোমার ই-মেইল আইডি]
৯. (খ) সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে 'মাঠকর্মী' হিসেবে চাকরির জন্য যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে একটি আবেদনপত্র:
বরাবর
পরিচালক,
সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর,
[সংশ্লিষ্ট জেলার নাম/ঢাকা, যদি কেন্দ্রীয়ভাবে হয়]
বিষয়: 'মাঠকর্মী' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।
জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত [তারিখ] তারিখে [পত্রিকার নাম/ওয়েবসাইটের নাম]-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারলাম যে, আপনার অধিদপ্তরের অধীনে 'মাঠকর্মী' পদে কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে আমার যোগ্যতার বিবরণ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।
আমার যোগ্যতার বিবরণ নিম্নরূপ:
-
নাম: [পূর্ণ নাম]
-
পিতার নাম: [পিতার নাম]
-
মাতার নাম: [মাতার নাম]
-
স্থায়ী ঠিকানা: [গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা]
-
বর্তমান ঠিকানা: [গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা]
-
জন্ম তারিখ: [দিন/মাস/বছর]
-
জাতীয়তা: বাংলাদেশি
-
ধর্ম: [ধর্ম]
-
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
-
এস.এস.সি. (ssc): [সাল], [বিভাগ/জি.পি.এ.], [বোর্ড]
-
এইচ.এস.সি. (Hsc): [সাল], [বিভাগ/জি.পি.এ.], [বোর্ড]
-
স্নাতক (Graduation): [সাল], [বিষয়/বিভাগ], [বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ]
-
-
অভিজ্ঞতা:
-
[যদি থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠানের নাম, পদের নাম, এবং কত বছর কাজ করেছেন তার বিবরণ দিন। যেমন: 'একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ২ বছর মাঠকর্মী হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা।']
-
-
বিশেষ দক্ষতা:
-
[মাঠকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যেমন: কম্পিউটার চালনায় মৌলিক জ্ঞান, যোগাযোগ দক্ষতা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে কাজ করার ক্ষমতা, মোটর সাইকেল চালনায় পারদর্শী ইত্যাদি।]
-
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাঠ পর্যায়ে কাজ করার আগ্রহ এবং নিষ্ঠা আমাকে এই পদের জন্য একজন উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে প্রমাণ করবে। আমি অত্যন্ত পরিশ্রমী, উদ্যমী এবং যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে সক্ষম।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমাকে উল্লিখিত পদে নিয়োগদানে আপনার সদয় মর্জি হয়।
বিনীত নিবেদক,
[আপনার স্বাক্ষর]
[আপনার পূর্ণ নাম]
[আপনার ফোন নম্বর]
[আপনার ই-মেইল আইডি]
সংযুক্তি:
১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি।
২. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
৩. সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি।
৪. অভিজ্ঞতার সনদপত্র (যদি থাকে)।
১০. (ক) সারাংশ:
মূল ভাব: দুঃখ মানুষকে বিশুদ্ধ করে এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করে। সুখের চেয়ে দুঃখই মানুষের অনুভূতিকে বেশি তীক্ষ্ণ ও সজাগ করে তোলে। ভুল করার মাধ্যমে প্রাপ্ত দুঃখ মানুষকে অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করে এবং আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যারা ভুল করেও নির্বিকার থাকে, তাদের কাছে সত্য-মিথ্যা বা পাপ-পুণ্যের কোনো মূল্য থাকে না।
সারাংশ:
মানুষের জীবনে দুঃখের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি সুখের চেয়েও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভুল থেকে প্রাপ্ত দুঃখ অনুশোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে এবং তার মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক হয়। যে ভুল করেও নির্বিকার থাকে, সে জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে পারে না। বস্তুত, দুঃখই মানুষকে সংবেদনশীল ও সচেতন করে তোলে।
১০. (খ) ভাব-সম্প্রসারণ: "প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।”
ভাব-সম্প্রসারণ:
মানব জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার কেবল তাদেরই, যারা প্রয়োজন হলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। এই উক্তিটি জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা, আত্মত্যাগ এবং সাহসের গভীর অর্থ বহন করে। এটি বোঝায় যে, শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে থাকাটাই জীবন নয়, বরং নীতি, আদর্শ, দেশ, বা সমাজের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা থাকলেই একজন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে বাঁচতে পারে এবং জীবনের মহিমা অনুভব করতে পারে।
সাধারণত, মানুষ জীবনকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে এবং বাঁচতে চায়। কিন্তু এমন কিছু পরিস্থিতি আসে যখন ব্যক্তি বা সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়। যেমন, দেশমাতৃকাকে রক্ষা করতে গিয়ে সৈনিকের আত্মদান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহীদের আত্মবলিদান, বা মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞানীর জীবন উৎসর্গ—এসবই প্রয়োজনে মরতে প্রস্তুত থাকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা এমন ত্যাগ স্বীকারে পিছপা হয় না, তারাই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকে এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়। তাদের জীবন ও আদর্শ অন্যদের বাঁচতে শেখায়, অনুপ্রাণিত করে।
বিপরীতক্রমে, যারা কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বাঁচে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বা মহৎ কোনো আহ্বানে নিজেদের জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা হয়তো দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে, কিন্তু তাদের সেই জীবন নিষ্ফল ও অর্থহীন। তাদের বাঁচা যেন এক ধরণের বোঝা, যা সমাজ বা অন্যদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। তাদের এই বেঁচে থাকা কেবল নিজের অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতাতেই আবদ্ধ থাকে, যা তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে দেয়।
সুতরাং, এই উক্তিটি কেবল বীরত্ব বা সাহসিকতার কথা বলে না, এটি জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোকপাত করে। প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতাই একজন মানুষকে প্রকৃত জীবন দেয় এবং তাকে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার প্রদান করে। এভাবেই ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর কল্যাণের অংশ হয়ে অমরত্ব লাভ করে।
১১. (ক) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ:
বাবা: কিরে মা, আজ স্কুলে কেমন কাটলো দিনটা? কোনো বিশেষ কিছু হলো নাকি?
মেয়ে (রিয়া): হ্যাঁ বাবা, একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমাদের নতুন ইতিহাস স্যার এসেছেন, উনি আজ ক্লাসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কথা বলছিলেন।
বাবা: ওহ, খুব ভালো তো! কী বলছিলেন তিনি?
রিয়া: তিনি বলছিলেন যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ কীভাবে যুগ যুগ ধরে মিলেমিশে থাকছে, একে অপরের উৎসবে অংশ নিচ্ছে। যেমন, দুর্গাপূজা বা ঈদ—সবাই যেন একই পরিবারের সদস্য।
বাবা: একদম ঠিক কথা। এটাই তো আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি, জানিস। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। সেই থেকেই আমাদের এই সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে।
রিয়া: হ্যাঁ, স্যার একটা গল্পও বললেন। আমাদের এলাকার মন্দিরের পাশে নাকি একটা মসজিদ আছে। দুটো জায়গাতেই প্রায় একই সময়ে প্রার্থনা হয়, কিন্তু কেউ কারো প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। বরং একজন আরেকজনকে সম্মান করে।
বাবা: এটাই তো হওয়া উচিত, মা। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমরা সবাই তো মানুষ। ধর্ম মানুষকে ভালো হতে শেখায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। কোনো ধর্মই হিংসা বা বিভেদ শেখায় না।
রিয়া: কিন্তু বাবা, মাঝেমধ্যে টিভিতে বা পত্রিকায় দেখি, কিছু মানুষ নাকি ধর্মের নামে ঝামেলা করে। এটা কেন হয়?
বাবা: সেটা কিছু অসাধু মানুষের কাজ, মা। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দেয় এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই শান্তিপ্রিয় এবং তারা সম্প্রীতি চায়। তুই দেখবি, যখন কোনো বিপদ আসে, তখন হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্মের ভেদাভেদ তখন আর থাকে না।
রিয়া: তাহলে আমাদের কী করা উচিত, বাবা? আমরা কীভাবে এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারি?
বাবা: খুব সহজ, মা। ছোটবেলা থেকেই নিজেদের পরিবারে এবং সমাজে আমরা যদি সবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বড় হই, সবার ধর্মকে সম্মান করি, তাহলেই এই সম্প্রীতি টিকে থাকবে। উৎসবগুলোতে অংশ নেওয়া, বিপদে পাশে দাঁড়ানো—এগুলোই তো সম্প্রীতির মূল মন্ত্র। তুই যেমন তোর মুসলিম বন্ধুর ঈদের সেমাই খেতে যাস, বা তোর খ্রিস্টান বন্ধুর বড়দিনের কেক খাস, ঠিক তেমনই।
রিয়া: হ্যাঁ বাবা, আমি বুঝলাম। স্যারও আজ বললেন, সম্প্রীতিই আমাদের এগিয়ে চলার পথ।
বাবা: একদম ঠিক বলেছিস। এটাই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। এই সম্প্রীতির মাধ্যমেই আমরা একটা সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।
১১. (খ) 'স্বনির্ভরতার জন্য দেশি শিল্পের বিকাশ চাই' শিরোনামে একটি খুদে গল্প:
স্বপ্ন পূরণের গ্রাম: সোনারগাঁও
একসময় সোনারগাঁও গ্রামটি ছিল এক নিস্তেজ ছবি। কৃষিকাজই ছিল গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা, কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি আর বন্যা তাদের জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। তরুণদের চোখে ছিল হতাশা, কাজের সন্ধানে সবাই ছুটছিল শহরের দিকে। গ্রাম যেন ধীরে ধীরে তার প্রাণ হারাচ্ছিল।
এই গ্রামেরই এক ছেলে, আবির। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে সে গ্রামে ফিরে আসে। তার মনে একটাই স্বপ্ন – গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করা। সে জানতো, বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে না পারলে গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। একদিন আবির গ্রামের প্রবীণদের নিয়ে বৈঠকে বসল। সে তাদের সামনে দেশি শিল্পের বিকাশের ধারণা তুলে ধরল। প্রথমে অনেকেই সন্দিহান ছিল। "আমরা কী পারবো?" "আমাদের তো পুঁজি নেই!" – এমন প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
কিন্তু আবির হাল ছাড়ার পাত্র ছিল না। সে দেখালো, তাদের গ্রামেই প্রচুর বাঁশ আছে, যা দিয়ে হস্তশিল্প তৈরি করা যায়। গ্রামের নারীরা কাঁথা সেলাইয়ে পারদর্শী, পুরুষরা কাঠের কাজ জানে। কেন তারা নিজেদের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে কাজে লাগাবে না? আবির স্থানীয় এনজিওর সাথে যোগাযোগ করে পুঁজির ব্যবস্থা করল এবং অল্প কিছু মানুষকে নিয়ে একটি কর্মশালা শুরু করল।
প্রথমদিকে বাঁশের খেলনা আর শখের হাঁড়ি তৈরি শুরু হলো। আবির নিজেই সেগুলো শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। প্রথমবার যখন তার তৈরি পণ্য বিক্রি হলো, তখন গ্রামের মানুষের চোখে আশার আলো ঝলমল করে উঠল। ধীরে ধীরে তারা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল। নারীরা রঙিন সুতোয় নকশা করা শাড়ি আর কাঁথা তৈরি করতে লাগল। পুরুষরা কাঠের আসবাবপত্র আর শো-পিস বানাতে শুরু করল।
আবির অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তাদের পণ্য বিক্রি শুরু করল। 'সোনারগাঁও হস্তশিল্প' নামে তাদের পরিচিতি বাড়তে লাগল। একসময় যে গ্রাম থেকে তরুণরা পালিয়ে যেত, এখন সেই গ্রামেই নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হলো। বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমে গেল, কারণ তাদের নিজেদের তৈরি পণ্যই ছিল মানসম্মত ও সুন্দর। সোনারগাঁও আর কেবল একটি গ্রাম ছিল না, এটি হয়ে উঠেছিল স্বনির্ভরতার এক প্রতীক, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের শ্রমে এবং দেশি শিল্পের বিকাশে নিজেদের জীবনকে নতুন অর্থ দিতে পেরেছিল। আবির প্রমাণ করে দিল, স্বপ্ন দেখলে এবং চেষ্টা করলে, নিজেদের মাটিতেও সোনার ফসল ফলানো সম্ভব।
১২. (গ) একুশের চেতনা:
একুশের চেতনা: মুক্তির পথে প্রথম পদধ্বনি
বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি এক অবিস্মরণীয় দিন, যা শুধু একটি তারিখ নয়, একটি চেতনার নাম। এটি আমাদের আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা এবং আত্মত্যাগের এক শাশ্বত প্রতীক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার প্রথম সাহসী পদক্ষেপ। এই আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকার আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার মন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।
একুশের পটভূমি ও তাৎপর্য:
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই অন্যায় সিদ্ধান্ত বাঙালির মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা আর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অদম্য বাসনা থেকে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই প্রতিবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয় যখন পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় এবং রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেকে শহীদ হন। এই আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি; তাদের বুকের রক্তে রঞ্জিত রাজপথেই অর্জিত হয়েছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ:
একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এটি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম সোপান। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিচয়ের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। 'আমরা বাঙালি'—এই স্লোগান সেদিন শুধু ভাষার জন্য উচ্চারিত হয়নি, বরং এটি ছিল একটি নবজাগরণের ঘোষণা। এই চেতনা পরবর্তীকালে স্বাধিকার আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং পরিশেষে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ভাষা আন্দোলনই দেখিয়েছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস থাকলে যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস:
একুশের আত্মত্যাগ আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এটি বাঙালির জন্য এক বিশাল অর্জন। এই স্বীকৃতি শুধু বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান নয়, বরং পৃথিবীর সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সংহতির প্রতীক। এখন এই দিনে সারা বিশ্বের মানুষ নিজ নিজ মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ভাষার অধিকার রক্ষায় সচেতন হয়।
একুশের চেতনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা:
একুশের চেতনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের শিখিয়েছে, অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার দৃঢ়তা। সমাজের প্রতিটি স্তরে আজও নানান ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি, এবং সাম্প্রদায়িকতা—এসবই একুশের চেতনার পরিপন্থী। একুশের চেতনা আমাদের এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। মাতৃভাষার সঠিক চর্চা ও এর সম্মান রক্ষা করা, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা, এবং একটি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমরা একুশের শহীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।
উপসংহার:
একুশ আমাদের অহংকার, আমাদের প্রেরণার উৎস। এটি শুধুমাত্র একটি অতীত ইতিহাস নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত শক্তি যা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে পথ দেখায়। একুশের চেতনাকে ধারণ করে আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করি, তাহলেই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ, থাকবে শুধু সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি।