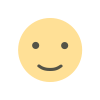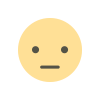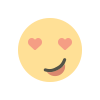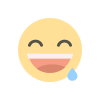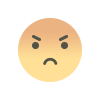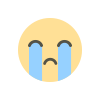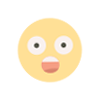এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। সিলেট বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। সিলেট বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
১. (ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:
বাংলা ভাষায় 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ দুই প্রকারের হয়: সংবৃত 'এ' (এ) এবং বিবৃত 'এ' (অ্যা)। এই দুটি উচ্চারণের ভিন্নতা কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের উপর নির্ভরশীল। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:
১. একাক্ষর শব্দের শেষে 'এ': একাক্ষর (এক syllable বিশিষ্ট) শব্দের শেষে 'এ' থাকলে সাধারণত তার উচ্চারণ সংবৃত হয়।
* উদাহরণ: কে (উচ্চারণ: কে), সে (উচ্চারণ: সে), নে (উচ্চারণ: নে)।
২. ক্রিয়া পদের 'এ': বর্তমান কালের সাধারণ ক্রিয়াপদে 'এ' সংবৃত উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ: খেলে (উচ্চারণ: খেলে), চলে (উচ্চারণ: চ'লে), বলে (উচ্চারণ: ব'লে)।
৩. তৎসম শব্দের 'এ': বহু তৎসম শব্দে 'এ' ধ্বনি সংবৃত থাকে।
* উদাহরণ: দেশ (উচ্চারণ: দেশ), প্রেম (উচ্চারণ: প্রেম), শেষ (উচ্চারণ: শেষ)।
৪. যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'এ': যদি 'এ' ধ্বনির পরে যুক্তব্যঞ্জন থাকে, তবে 'এ' সংবৃত উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ: রেলপথ (উচ্চারণ: রেলপথ), একত্র (উচ্চারণ: এক্-ত্রো)।
৫. বিশেষ্য শব্দের আদিতে 'এ' (কিছু ক্ষেত্রে বিবৃত): যদি শব্দের আদিতে 'এ' বসে এবং তারপর একটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ আসে, তাহলে সাধারণত 'এ' বিবৃত উচ্চারিত হয়। তবে এটি সবসময় হয় না।
* উদাহরণ: এক (উচ্চারণ: অ্যাঁক), একরোখা (উচ্চারণ: অ্যাঁক্রোখা)।
* (ব্যতিক্রম: বেলা (উচ্চারণ: বেলা), দেখা (উচ্চারণ: দেখা), এখানে 'এ' সংবৃত।)
১. (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ:
-
অধ্যক্ষ: ওদ্ধোক্খো
-
উদ্যোগ: উদজোগ্
-
ব্যাখ্যা: ব্যাক্খা
-
ঋগ্বেদ: রিগ্বেদ
-
যজ্ঞ: জজ্ঞো
-
সভ্য: শোব্ভো
-
স্মর্তব্য: শ্মোর্তোব্বো
-
ভবিষ্যৎ: ভোবিশ্শোঁত্
২. (ক) আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:
আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার (ি) ব্যবহারের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, যা বানান সরলীকরণ ও শৃঙ্খলা আনয়নে সহায়ক। নিচে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উদাহরণসহ দেওয়া হলো:
১. সকল অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দে ই-কার: বাংলা একাডেমি আধুনিক বানানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তৎসম নয় এমন সব শব্দে (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং মিশ্র) সর্বদা ই-কার (ি) ব্যবহৃত হবে, এমনকি যেখানে পূর্বে ঈ-কার (ী) ব্যবহৃত হতো।
* উদাহরণ: সরকারি, কুমির, চিরুনি, শাড়ি, স্টিমার, নভেম্বর, জানুয়ারি, ফুটবল, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি, বাঙালি, খ্রিস্টাব্দ।
২. রেফ-এর পর ই-কার: রেফ-এর পর ই-কার বসবে, ঈ-কার নয়।
* উদাহরণ: কারিগর, সরকারি, ফর্দি।
৩. আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার: 'আলি' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে।
* উদাহরণ: মিতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, বর্ণালি, সোনালি।
৪. বিশেষণ পদ গঠনে ই-কার: কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ্য পদ থেকে বিশেষণ পদ গঠন করার সময় ই-কার ব্যবহার করা হয়।
* উদাহরণ: জাতি থেকে জাতীয়, পরিবার থেকে পারিবারিক।
৫. স্ত্রীবাচক শব্দে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) ই-কার: আধুনিক বানানে স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ-কার ব্যবহারের প্রবণতা কমে গিয়ে ই-কার ব্যবহারের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে কিছু তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ-কার ব্যবহৃত হতে পারে।
* উদাহরণ: শিক্ষিকা, লেখিকা, ছাত্রী (আগে 'ছাত্রী'তে ঈ-কার থাকলেও আধুনিক বানানে এর চল কমেছে, যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়নি। মূলত, স্ত্রীবাচক 'ইনী' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দেও ই-কার)।
২. (খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
-
ইতিপূর্বে ইতিপূর্বে (শুদ্ধ বানান এটিই)
-
মুহূর্ত মুহূর্ত (শুদ্ধ বানান এটিই)
-
পিপীলিকা পিপীলিকা (শুদ্ধ বানান এটিই)
-
গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি ('অঞ্জলি'তে ই-কার হয়, তাই এটি শুদ্ধ)
-
পোস্টমাস্টার পোস্টমাস্টার (ইংরেজি 'Postmaster' থেকে এসেছে, 'ষ' না হয়ে 'স' হবে)
-
পাণিনি পাণিনি ('ন' এর পরিবর্তে 'ণ' হবে)
-
স্বাতন্ত্র্য স্বাতন্ত্র্য ('সাতন্ত্র' ভুল বানান)
-
ন্যূনতম ন্যূনতম ('নুন্যতম' ভুল বানান)
৩. (ক) উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা:
ক্রিয়াপদ হলো সেই পদ যা দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া, বা ঘটা বোঝায়। একটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে ক্রিয়াপদ অপরিহার্য।
উদাহরণ:
-
ছেলেটি বই পড়ছে। (এখানে 'পড়ছে' দ্বারা একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে।)
-
সূর্য উঠছে। (এখানে 'উঠছে' দ্বারা একটি ঘটনা ঘটা বোঝাচ্ছে।)
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:
১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং বাক্য শেষ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: সে ভাত খায়। (এখানে 'খায়' ক্রিয়াটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করেছে।)
২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না এবং বাক্যটি আরও কিছু অংশের উপর নির্ভর করে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সাধারণত এই ক্রিয়ার শেষে 'ইয়ে', 'লে', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত থাকে।
* উদাহরণ: সে খেয়ে ঘুমালো। (এখানে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া, যা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করেনি।)
৩. সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, অর্থাৎ যাকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। (এখানে 'কী খাওয়াচ্ছেন?' - 'দুধ', 'কাকে খাওয়াচ্ছেন?' - 'শিশুকে'; তাই 'খাওয়াচ্ছেন' সকর্মক ক্রিয়া।)
৪. অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, অর্থাৎ যাকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: মেয়েটি হাসে। (এখানে 'কী হাসে?' বা 'কাকে হাসে?' - কোনো উত্তর নেই; তাই 'হাসে' অকর্মক ক্রিয়া।)
৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে (একটি মুখ্য কর্ম এবং একটি গৌণ কর্ম), তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়।
* উদাহরণ: বাবা আমাকে একটি কলম দিলেন। (এখানে 'আমাকে' গৌণ কর্ম এবং 'কলম' মুখ্য কর্ম।)
৬. যৌগিক ক্রিয়া: দুটি ক্রিয়াপদ একত্রিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। এর গঠন সাধারণত একটি অসমাপিকা ক্রিয়া + একটি সমাপিকা ক্রিয়া।
* উদাহরণ: সে বই পড়তে লাগল। (এখানে 'পড়তে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'লাগল' সমাপিকা ক্রিয়া মিলে যৌগিক ক্রিয়া।)
৭. প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজটি করায়, তখন তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
* উদাহরণ: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। (এখানে মা নিজে চাঁদ দেখছেন না, শিশুকে দেখাচ্ছেন।)
৩. (খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ চিহ্নিত কর:
বিশেষণ শব্দ সেই পদ যা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে।
অনুচ্ছেদ: অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও-আমি বলতে চাইনা। অপবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর-তাহলেই অনেক হবে।
চিহ্নিত পাঁচটি বিশেষণ শব্দ:
১. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (দুঃখের পরিমাণ/অবস্থা বোঝাচ্ছে)
২. একটুখানি (সুখের পরিমাণ বোঝাচ্ছে)
৩. মিষ্টি (কথার গুণ বোঝাচ্ছে)
৪. অসহায় (মানুষটির অবস্থা বোঝাচ্ছে)
৫. করুণ (দৃষ্টির গুণ/অবস্থা বোঝাচ্ছে)
৪. (ক) উপসর্গ কী? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর:
উপসর্গ কী?
উপসর্গ হলো কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ যা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, বা সংকোচন ঘটায়। উপসর্গের নিজস্ব কোনো স্বাধীন বা একক অর্থ নেই, তবে এরা যখন কোনো শব্দের আগে বসে, তখন তার অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ দ্যোতনা বা নতুনত্ব সৃষ্টি করে।
উদাহরণ: 'হার' একটি শব্দ। এর আগে 'প্র' বসিয়ে হয় 'প্রহার' (অর্থ: আঘাত করা), 'উপ' বসিয়ে হয় 'উপহার' (অর্থ: ভেট), 'আ' বসিয়ে হয় 'আহার' (অর্থ: খাওয়া)। এখানে 'প্র', 'উপ', 'আ' প্রত্যেকেই উপসর্গ।
উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা:
বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর মূল কারণগুলো হলো:
১. নতুন শব্দ গঠন: উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে, যা ভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এটি একটি ভাষাভাষী মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশে বৈচিত্র্য আনে।
* উদাহরণ: দান (প্রদান, অবদান), নাম (প্রণাম, অনাম)।
২. অর্থের পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ: উপসর্গের প্রধান কাজ হলো মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ ঘটানো। এটি মূল অর্থকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে।
* উদাহরণ: 'পাক' (পরিষ্কার) থেকে পরিষ্কার (সম্পূর্ণ পরিষ্কার), পাকানো (কোনো কিছু পাকানো)।
৩. অর্থের সংকোচন: কখনও কখনও উপসর্গ মূল শব্দের অর্থকে সংকুচিত করে একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রকাশ করে।
* উদাহরণ: 'জল' (পানি) থেকে সজল (জলসহ, আর্দ্র)।
৪. অর্থের পূর্ণতা দান: অনেক সময় উপসর্গ শব্দের অর্থকে পূর্ণতা দান করে বা তার ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে তোলে।
* উদাহরণ: 'পূর্ণ' থেকে সম্পূর্ণ (পুরোপুরি পূর্ণ)।
৫. ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি: নতুন শব্দ গঠন এবং অর্থের বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে উপসর্গ বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গি এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এটি সাহিত্য ও কাব্যে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
৬. ভাব প্রকাশে সূক্ষ্মতা: একই মূল শব্দ থেকে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যা ভাষা ব্যবহারের নমনীয়তা বাড়ায়।
* উদাহরণ: 'গতি' (চলা) থেকে প্রগতি (অগ্রগতি), দুর্গতি (খারাপ অবস্থা)।
উপসংহারত, যদিও উপসর্গের নিজস্ব কোনো স্বাধীন অর্থ নেই, তবুও তারা বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি, অর্থের পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ভাষার প্রকাশভঙ্গিকে অধিক সমৃদ্ধ ও কার্যকর করে তোলে। এই কারণেই উপসর্গের ব্যবহার বাংলা ব্যাকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৪. (খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে কোনো পাঁচটি):
সমাস হলো দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করার প্রক্রিয়া, যার ফলে একটি নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়। নিচে প্রদত্ত শব্দগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করা হলো:
-
পদ্মআঁখি:
-
ব্যাসবাক্য: পদ্মের ন্যায় আঁখি যার
-
সমাস: উপমান বহুব্রীহি সমাস
-
-
নদীমাতৃক:
-
ব্যাসবাক্য: নদী মাতা যার
-
সমাস: বহুব্রীহি সমাস
-
-
হজ্বযাত্রা:
-
ব্যাসবাক্য: হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা
-
সমাস: চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
-
-
ক্রোধানল:
-
ব্যাসবাক্য: ক্রোধ রূপ অনল
-
সমাস: রূপক কর্মধারয় সমাস
-
-
ঢেঁকিছাটা:
-
ব্যাসবাক্য: ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা
-
সমাস: তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
-
-
দম্পতি:
-
ব্যাসবাক্য: জায়া ও পতি
-
সমাস: দ্বন্দ্ব সমাস (কিছু ব্যাকরণবিদ এটিকে নিত্য সমাসও বলেন, তবে প্রচলিত অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস।)
-
-
ধর্মঘট:
-
ব্যাসবাক্য: ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ঘট
-
সমাস: মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস (ধর্মরক্ষার্থে কর্মের প্রতি ঘট)
-
-
বজ্রকঠোর:
-
ব্যাসবাক্য: বজ্রের ন্যায় কঠোর
-
সমাস: উপমান কর্মধারয় সমাস
-
৫. (ক) একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ:
একটি বাক্য তখনই সার্থক হয় যখন তা বক্তার মনোভাবকে স্পষ্টভাবে, সঙ্গতিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি প্রধান গুণ থাকা আবশ্যক: আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।
১. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যস্থিত একটি পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা জাগে, তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যদি কোনো বাক্যে এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়, তাহলে বাক্যটি অসম্পূর্ণ বা অসার্থক মনে হয়।
* উদাহরণ:
* অসার্থক বাক্য: "আমি ভাত" (এখানে 'খাই' বা অন্য কোনো ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে।)
* সার্থক বাক্য: "আমি ভাত খাই।" (এখানে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে।)
২. আসত্তি (বা নৈকট্য): বাক্যের পদগুলোকে অর্থগত সঙ্গতি রেখে পরপর সাজানোকে আসত্তি বলে। অর্থাৎ, বাক্যের পদগুলোর বিন্যাস এমন হতে হবে যেন তাদের মধ্যে অর্থগত একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। পদগুলোর সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত সন্নিবেশ না হলে বাক্যটি সার্থক হয় না।
* উদাহরণ:
* অসার্থক বাক্য: "ঘরে কাল যাব আমি।" (পদগুলো এলোমেলো।)
* সার্থক বাক্য: "আমি কাল ঘরে যাব।" (পদগুলো সুবিন্যস্ত।)
৩. যোগ্যতা: বাক্যের পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত সঙ্গতিকে যোগ্যতা বলে। অর্থাৎ, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে। এমন কোনো শব্দ বা ভাব ব্যবহার করা যাবে না যা বাস্তবে অসম্ভব বা অযৌক্তিক।
* উদাহরণ:
* অসার্থক বাক্য: "সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে।" (বাস্তবে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, তাই এটি যোগ্যতাহীন বাক্য।)
* সার্থক বাক্য: "সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।" (এটি বাস্তবসম্মত ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য।)
এই তিনটি গুণ থাকলে একটি বাক্য তার অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং তা সার্থক বাক্য হিসেবে বিবেচিত হয়।
৫. (খ) নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যে কোনো পাঁচটি):
বাক্যান্তর বলতে এক প্রকার বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করাকে বোঝায়, যেখানে মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। নিচে নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তরিত করা হলো:
(i) ধনির কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: ধনির কন্যা তার অপছন্দ।
(ii) এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: এখানে না এসে পারলাম না।
(iii) মৃত্যুই জীবনের শেষ। (প্রশ্নবোধক)
* রূপান্তরিত বাক্য: মৃত্যুই কি জীবনের শেষ?
(iv) "ইহারা যেরপ. এরপ রপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।" (সরল)
* রূপান্তরিত বাক্য: আমার অন্তঃপুরে এরূপ রূপবতী রমণী নাই।
(v) যে লোকটি এখানে এসেছিল সে আমার ভাই। (যৌগিক)
* রূপান্তরিত বাক্য: লোকটি এখানে এসেছিল এবং সে আমার ভাই।
(vi) কেন সময় নষ্ট কর? (নির্দেশাত্মক)
* রূপান্তরিত বাক্য: সময় নষ্ট করো না।
(vii) নির্বোধকে এত বুঝিয়ো না। (জটিল)
* রূপান্তরিত বাক্য: যে নির্বোধ, তাকে এত বুঝিয়ো না।
(viii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)
* রূপান্তরিত বাক্য: বিপদে অধীর হয়ো না।
৬. (ক) যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
বাক্য শুদ্ধিকরণ হলো ব্যাকরণগত ত্রুটি, বানান ভুল বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার পরিহার করে একটি বাক্যের সঠিক ও সুন্দর রূপ দেওয়া। নিচে প্রদত্ত বাক্যগুলোর শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো:
(i) নদীর জল কমে গেছে। ('হ্রাস হয়েছে' এর চেয়ে 'কমে গেছে' বেশি প্রচলিত ও সহজবোধ্য।)
(ii) এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না। (বাক্যটি ইতোমধ্যে শুদ্ধ। 'মোকদ্দমা'র পরিবর্তে 'মামলা' বেশি প্রচলিত।)
(iii) আজীবন দেশের সেবা করে যাব। ('আমৃত্যু পর্যন্ত' বাহুল্য দোষে দুষ্ট। 'আমৃত্যু' অথবা 'মৃত্যু পর্যন্ত' ব্যবহৃত হতে পারে। 'আজীবন' আরও উপযুক্ত।)
(iv) বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ('উন্নতশীল' এর বদলে 'উন্নয়নশীল' হবে, যা চলমান উন্নয়নের প্রক্রিয়া বোঝায়।)
(v) মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে। ('বিদ্বান' পুরুষবাচক শব্দ, নারীবাচক শব্দ হবে 'বিদুষী'।)
(vi) এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। ('প্রমাণ হয়েছে' এর চেয়ে 'প্রমাণিত হয়েছে' ব্যাকরণগতভাবে অধিক শুদ্ধ।)
(vii) ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। ('দুর্দান্ত' শব্দটি সাধারণত নেতিবাচক বা অতি-উৎসাহব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়, মেধাবীর ক্ষেত্রে 'অত্যন্ত' বা 'খুব' উপযুক্ত।)
(viii) আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। ('চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ' বাহুল্য দোষে দুষ্ট, কারণ 'চাক্ষুষ' অর্থই হলো 'চোখের দ্বারা দেখা' বা 'প্রত্যক্ষ করা'।)
৬. (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:
অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভুল বানান, ব্যাকরণগত ত্রুটি এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার শুদ্ধ করে নিচে লেখা হলো:
আজকাল বানানের ব্যাপারে সব ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা তো সচেষ্ট নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
বিশ্লেষণ ও শুদ্ধিকরণ:
-
আজিকাল আজকাল: সঠিক বানান।
-
সকল ছাত্ররাই সব ছাত্রই: 'সকল' এবং 'ছাত্ররাই' একসাথে দ্বিরুক্তি বা বাহুল্য দোষ তৈরি করেছে। 'সব ছাত্রই' বা 'সকল ছাত্র' হতে পারে। এখানে 'সব ছাত্রই' বেশি শ্রুতিমধুর।
-
তাহারা তারা: আধুনিক চলিত বাংলায় 'তাহারা' না হয়ে 'তারা' ব্যবহৃত হয়।
-
নহেই নয়ই: ক্রিয়াপদের ভুল ব্যবহার। 'নয়ই' সঠিক।
-
অবস্থাদৃষ্টে অবস্থা দেখে: 'অবস্থাদৃষ্টে' একটি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দ, যা এই সরল চলিত অনুচ্ছেদে বেমানান। 'অবস্থা দেখে' বা 'পরিস্থিতি দেখে' অধিক চলিত ও উপযুক্ত।
-
ভূল ভুল: সঠিক বানান।
-
প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগিতায়: সঠিক বানান।
৭. (ক) যে কোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ:
পারিভাষিক শব্দ হলো বিশেষ অর্থ বহনকারী শব্দ যা নির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্র, পেশা বা কারিগরি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রদত্ত ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক রূপ দেওয়া হলো:
-
Aid: সাহায্য / সহায়তা
-
Book-post: খোলা ডাক
-
Cartoon: ব্যঙ্গচিত্র
-
Embargo: অবরোধ
-
Fiction: কথাসাহিত্য / কল্পকাহিনী
-
Ad-hoc: অনানুষ্ঠানিক / তদর্থক
-
Memorandum: স্মারকলিপি
-
Circle: বৃত্ত / মণ্ডল / চক্র
-
Worship: উপাসনা / পূজা
-
Manuscript: পাণ্ডুলিপি
-
Tribunal: ট্রাইব্যুনাল / বিচারসভা
-
Dialect: উপভাষা
-
Racism: বর্ণবাদ
-
Catalogue: ক্যাটালগ / সূচি
-
Up-to-date: হালনাগাদ
৭. (খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ:
Early rising is beneficial to health. The boy who rises early enjoy the fine air of the morning. He can take a walk by the river side or in the open field. He can enjoy sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.
অনুবাদ:
ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। যে ছেলে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে, সে সকালের নির্মল বাতাস উপভোগ করে। সে নদীর ধারে বা খোলা মাঠে হাঁটতে পারে। সে পাখির মিষ্টি গান শুনতে এবং সূর্যোদয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারে। এই সবকিছু তাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখে।
৮. (ক) পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন অবলম্বনে একটি দিনলিপি:
১৪ই এপ্রিল, ২০২৫, সোমবার
রাত ১০:৩০টা
আজ নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিন, পহেলা বৈশাখ। সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন আনন্দে ভরে ছিল। পুরো শহরটাই যেন সেজে উঠেছিল নতুন সাজে। গত কয়েকদিন ধরেই এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম।
সকালে ঘুম থেকে উঠেই গোসল সেরে নতুন জামা পরলাম। মা ইলিশ ভাজা আর পান্তা ভাতের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে পান্তা-ইলিশ খেলাম। সকালের এই পরিবেশটাই মনকে দারুণ সতেজ করে তুলল। এরপর বাবা-মায়ের সাথে বের হলাম মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখতে। শহরের প্রধান সড়কে মানুষের ঢল নেমেছিল। বর্ণিল পোশাক পরা নারী-পুরুষ, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আর বিভিন্ন লোকজ সজ্জা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। মুখোশ, মাটির পুতুল, আর বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি দেখতে দেখতে এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার অংশ।
শোভাযাত্রা শেষে আমরা মেলায় গেলাম। চারিদিকে নানা রঙের পসরা বসেছে। মাটির খেলনা, হাতের চুড়ি, চুড়ি ফিতা, আর হরেক রকমের পিঠা-পুলি। একটা দোকান থেকে মাটির সরা কিনলাম, যেখানে বাংলাদেশের লোকচিত্র আঁকা ছিল। বন্ধুদের সাথে দেখা হলো, সবাই মিলে ফুচকা খেলাম আর আড্ডা দিলাম। এই দিনটায় সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করে, যা সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়। কোনো ভেদাভেদ নেই, আছে শুধু বাঙালির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা।
বিকেলের দিকে কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল, তবুও মনটা ছিল ফুরফুরে। বাড়িতে ফিরেও বৈশাখী গানের সুর ভেসে আসছিল। সারাদিনের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস আমার মনকে এক অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে দিয়েছে। নতুন বছর যেন সবার জন্য শান্তি আর সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, এই কামনাই করি। পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে এক নতুন প্রেরণা, এক নতুন আশার আলো।
৮. (খ) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন:
প্রতিবেদন
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: জনজীবনে প্রভাব ও সম্ভাব্য প্রতিকার
তারিখ: ২৯শে জুন, ২০২৫
স্থান: চট্টগ্রাম
ভূমিকা:
বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, সবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ধারণকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ:
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান:
-
উৎপাদন ঘাটতি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলের রোগবালাই, বা কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়, ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ কমে যায়।
-
পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি: জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি পরিবহন ব্যয়কে বাড়িয়ে দেয়, যার প্রভাব পড়ে পণ্যের মূল্যে।
-
মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য: কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে মধ্যস্বত্বভোগীরা বিভিন্ন হাত ঘুরে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করে, যা মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
-
মজুদদারি ও সিন্ডিকেট: একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্য মজুদ করে রাখে এবং পরে চড়া দামে বিক্রি করে।
-
আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব: বিশ্ববাজারে কোনো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হলে তার প্রভাব স্থানীয় বাজারেও পড়ে।
-
মুদ্রাস্ফীতি: অর্থনীতির সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতিও পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।
-
দুর্বল বাজার তদারকি: সরকারি বাজার মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতা অসাধু ব্যবসায়ীদের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়।
জনজীবনে প্রভাব:
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে:
-
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি: সীমিত আয়ের মানুষের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে পড়ে।
-
পুষ্টিহীনতা: দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না, ফলে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়।
-
সংসার পরিচালনায় হিমশিম: বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের মাসিক বাজেট মেটাতে গিয়ে হিমশিম খায়।
-
সামাজিক অস্থিরতা: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমাজে অসন্তোষ ও অস্থিরতা বাড়ায়।
-
দারিদ্র্য বৃদ্ধি: অনেক পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়।
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা:
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:
-
উৎপাদন বৃদ্ধি: কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, উন্নত বীজ ও সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
-
সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা: উৎপাদনস্থল থেকে সরাসরি ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমানো যায়।
-
বাজার তদারকি জোরদার: নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
-
কঠোর আইন প্রয়োগ: মজুদদারি, সিন্ডিকেট এবং মূল্য কারসাজির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা।
-
জ্বালানি নীতির স্থিতিশীলতা: জ্বালানি তেলের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বা ভর্তুকি প্রদান করে পরিবহন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।
-
রেশন ব্যবস্থার প্রসার: স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির রেশন বা ওএমএস (Open Market Sale) ব্যবস্থা জোরদার করা।
-
জনসচেতনতা বৃদ্ধি: ভোক্তাদের সচেতন করে তোলা, যাতে তারা মূল্য কারসাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।
উপসংহার:
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি জটিল সমস্যা, যার সমাধান একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার, ব্যবসায়ী, এবং ভোক্তাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে দেশের অর্থনীতি ও জনজীবন আরও সংকটের মুখে পড়বে।
৯. (ক) বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি:
বিষয়: নববর্ষের শুভেচ্ছা!
প্রিয় [বন্ধুর নাম],
কেমন আছিস? আশা করি ভালো আছিস।
তোকে এবং তোর পরিবারের সবাইকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১-এর অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভ নববর্ষ!
পহেলা বৈশাখ মানেই নতুন দিনের সূচনা, নতুন আশা আর নতুন উদ্দীপনা। পুরনো দিনের সব দুঃখ, ক্লান্তি আর জঞ্জাল ভুলে গিয়ে নতুন করে পথচলার এই দিনটা সত্যিই খুব আনন্দের। আমি জানি, তুইও এই দিনটাকে খুব উপভোগ করিস।
আমরা আজ সকালে পান্তা-ইলিশ খেয়েছি, আর বিকেলে মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। চারিদিকে একটা উৎসবের আমেজ, মানুষের ভিড় আর হাসি-খুশির কোলাহল—সব মিলিয়ে দারুণ একটা দিন কেটেছে। তুই কী করছিস আজ? তোর ওখানে পহেলা বৈশাখ কীভাবে উদযাপন হচ্ছে, জানতে খুব ইচ্ছা করছে।
আশা করি নতুন বছর তোর জন্য অনেক সুখ, শান্তি আর সাফল্য বয়ে আনবে। তোর সব স্বপ্ন পূরণ হোক, এই কামনাই করি। সময় পেলে দেখা করিস বা ফোন করিস।
অনেক অনেক ভালোবাসা নিস।
শুভেচ্ছান্তে,
[তোমার নাম]
[তোমার ই-মেইল আইডি]
[তোমার মোবাইল নম্বর]
৯. (খ) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'হিসাবরক্ষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র:
বরাবর
ব্যবস্থাপক, মানবসম্পদ বিভাগ,
[প্রতিষ্ঠানের নাম]
[প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা]
বিষয়: 'হিসাবরক্ষক' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।
জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত [তারিখ] তারিখে [পত্রিকার নাম/ওয়েবসাইটের নাম]-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে 'হিসাবরক্ষক' পদে কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে আমার যোগ্যতার বিবরণ আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।
আমার শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার বিবরণ নিম্নরূপ:
-
নাম: [আপনার পূর্ণ নাম]
-
পিতার নাম: [পিতার নাম]
-
মাতার নাম: [মাতার নাম]
-
স্থায়ী ঠিকানা: [গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা]
-
বর্তমান ঠিকানা: [গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা]
-
জন্ম তারিখ: [দিন/মাস/বছর]
-
জাতীয়তা: বাংলাদেশি
-
ধর্ম: [ধর্ম]
-
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
-
এস.এস.সি. (ssc): [সাল], [বিভাগ/জি.পি.এ.], [বোর্ড]
-
এইচ.এস.সি. (Hsc): [সাল], [বিভাগ/জি.পি.এ.], [বোর্ড]
-
স্নাতক (হিসাববিজ্ঞান/ব্যবস্থাপনা/ফাইন্যান্স): [সাল], [প্রাপ্ত সিজিপিএ/বিভাগ], [বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ]
-
[যদি থাকে, স্নাতকোত্তর বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি উল্লেখ করুন]
-
-
কম্পিউটার দক্ষতা:
-
মাইক্রোসফট অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) এ পারদর্শী।
-
হিসাবরক্ষণের সফটওয়্যার যেমন Tally, QuickBooks বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যারে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
-
-
অভিজ্ঞতা:
-
[যদি থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠানের নাম, পদের নাম, এবং কত বছর কাজ করেছেন তার বিবরণ দিন। যেমন: 'গত [সময়কাল, যেমন: ২ বছর] যাবত [পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম]-এ হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।']
-
আমি একজন কর্মঠ, বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি। হিসাবরক্ষণের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে আমার স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে এবং আমি যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার দক্ষতা ও নিষ্ঠা আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সহায়ক হবে।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা, উল্লিখিত পদে আমাকে নিয়োগদানে আপনার সদয় মর্জি হয়।
বিনীত নিবেদক,
[আপনার স্বাক্ষর]
[আপনার পূর্ণ নাম]
[আপনার ফোন নম্বর]
[আপনার ই-মেইল আইডি]
সংযুক্তি:
১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
২. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি।
৪. অভিজ্ঞতার সনদপত্র (যদি থাকে)।
৫. জীবনবৃত্তান্ত (CV)।
১০. (ক) সারমর্ম:
মূলভাব: এখানে কবি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের কাছে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন। সোনার ধানে ভরা তরী চলে গেলেও, জীবন ও কর্মের সার্থকতা রয়ে যায়, কিন্তু নশ্বর জীবনে সবকিছু ধরে রাখা যায় না। সব কর্মফল মহাকালের স্রোতে বিলীন হলেও, তার বীজ নতুন রূপে ফিরে আসে, তবে মানুষ তার শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে বিচ্ছিন্ন ও অসহায়ভাবে পড়ে থাকে।
সারমর্ম:
জীবনের সকল অর্জন ও কর্মফল মহাকালের গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়, ঠিক যেমন ভরা তরী চলে গেলে তীরে অসহায় মাঝি পড়ে থাকে। মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মাঝে এক চিরায়ত শূন্যতা বিদ্যমান। মানুষ তার সকল চেষ্টা ও ফসল দিয়ে জীবনতরী ভরে তুললেও, একাকীত্বের বোঝা তাকে বহন করতে হয় এবং সে উপলব্ধি করে যে, প্রাপ্তি কেবল ক্ষণিকের, জীবনের শেষলগ্নে সবকিছুই চলে যায়, কিছুই স্থায়ী থাকে না।
১০. (খ) ভাব-সম্প্রসারণ: "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"
ভাব-সম্প্রসারণ:
মানুষ সামাজিক জীব। একা বা বিচ্ছিন্নভাবে তার পক্ষে বেঁচে থাকা বা উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব ও কল্যাণ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" – এই অমিয় বাণীটি মানব সমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা এবং পরোপকারের এক গভীর দর্শনকে তুলে ধরে। এটি বোঝায় যে, সমাজের প্রতিটি সদস্যই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা অন্যের কল্যাণের মধ্যেই নিহিত।
আমরা জন্ম থেকেই পরিবার, সমাজ এবং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল। আমাদের খাদ্যের সংস্থান থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বিনোদন—সবকিছুই সমাজের বিভিন্ন মানুষের শ্রম ও অবদানের ফল। কৃষক ফসল ফলায়, শ্রমিক কল-কারখানায় উৎপাদন করে, শিক্ষক জ্ঞান দান করেন, চিকিৎসক সেবা দেন—এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের জন্য কিছু না কিছু অবদান রাখে। এই পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি সমাজ সুসংগঠিত হয় এবং এগিয়ে চলে।
যদি আমরা কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, যদি প্রত্যেকে কেবল নিজের জন্য বাঁচে, তাহলে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, যা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, সামগ্রিক অগ্রগতিকেও বাধাগ্রস্ত করে। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যখনই কোনো সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তখনই তা সভ্যতা ও অগ্রগতির শিখরে পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে, বিভেদ ও স্বার্থপরতা প্রতিটি সমাজকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
পরের তরে জীবন উৎসর্গ করার অর্থ শুধু আত্মবলিদান নয়, বরং এটি দৈনন্দিন জীবনে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করাকেও বোঝায়। একজন প্রতিবেশী যখন বিপদে পড়ে, তার পাশে দাঁড়ানো; একজন সহকর্মী যখন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে, তাকে সাহায্য করা; সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো—এগুলোই হলো 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই চেতনার বাস্তব প্রতিফলন। এই উদার ও পরোপকারী মনোভাবই মানব সমাজের ভিত্তি মজবুত করে এবং সকলের জন্য একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে।
অতএব, এই মহৎ বাণীটি মানব জীবনের সার্থকতা এবং সামাজিক অস্তিত্বের মূল মন্ত্র। এটি আমাদের শেখায় যে, নিজের মঙ্গল অপরের মঙ্গলের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা যদি একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল ও সহনশীল হই, তাহলেই ব্যক্তিগত জীবন এবং সামগ্রিক সমাজ জীবন উভয়ই সমৃদ্ধ হবে।
১১. (ক) গণতন্ত্রের উত্তরণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ:
[স্থান: একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন]
[সময়: বিকাল ৪:৩০টা]
রফিক: কিরে আরিফ, আজ দুপুরের টিভিতে দেখলাম, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা টক-শো হচ্ছিল। তোর কী মনে হয়, আমাদের দেশে গণতন্ত্র কতটা এগিয়েছে?
আরিফ: হ্যাঁ, আমি নিজেও দেখছিলাম। আসলে গণতন্ত্রের উত্তরণ একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া, রফিক। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চলছে। কখনো সামরিক শাসন, কখনো আবার একদলীয় শাসন—অনেক উত্থান-পতন পেরিয়েছি আমরা।
রফিক: একদম ঠিক। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গণতন্ত্রের অবস্থা কেমন দেখছিস? নির্বাচন ব্যবস্থা, সুশাসন বা মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা—এসব বিষয়ে তোর পর্যবেক্ষণ কী?
আরিফ: সত্যি বলতে, এখনো অনেক পথ বাকি। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে মাঝে মাঝে, বিরোধী দলের মত প্রকাশের সুযোগ কতটা থাকে, তা নিয়েও বিতর্ক আছে। সুশাসনের দিক থেকেও চ্যালেঞ্জ আছে, যেমন দুর্নীতি দমন বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
রফিক: হ্যাঁ, তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ বেশ ভালো করছে। জিডিপি বাড়ছে, অবকাঠামোগত উন্নয়নও হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কি গণতন্ত্রের উত্তরণে সাহায্য করে না?
আরিফ: অবশ্যই করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীলতা আনে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। যখন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়, তখন তারা রাজনৈতিক অধিকার ও সুশাসন নিয়ে বেশি সচেতন হয়। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।
রফিক: তুই ঠিকই বলেছিস। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন শক্তিশালী সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, এবং মুক্ত গণমাধ্যম—এগুলো ছাড়া গণতন্ত্র মজবুত হয় না। আমাদের দেশে এসব ক্ষেত্রে আরও অনেক উন্নতির প্রয়োজন।
আরিফ: হ্যাঁ, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নাগরিকদের অংশগ্রহণ। মানুষ যদি ভোট দিতে না পারে বা তাদের মতামত প্রকাশ করতে ভয় পায়, তাহলে গণতন্ত্র তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হারায়। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করা খুব জরুরি।
রফিক: তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, গণতন্ত্রের উত্তরণ এখনো পুরোপুরি হয়নি, তবে প্রক্রিয়াটা চলছে?
আরিফ: আমার মনে হয়, সেটাই বলা যায়। আমরা এখন একটা ক্রান্তিকাল পার করছি। চ্যালেঞ্জগুলো অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। তরুণ প্রজন্ম এখন আরও বেশি গণতন্ত্রমনস্ক। আশা করি, আগামীতে আমরা আরও পরিপক্ব একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে পাবো। তবে এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
রফিক: তোর কথাগুলো যুক্তিযুক্ত। গণতন্ত্রকে মজবুত করতে হলে আমাদের সবাইকে যার যার জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।
আরিফ: একদম। চল, এখন উঠে পড়ি। সন্ধ্যা হয়ে এলো।
১১. (খ) 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম' শিরোনামে একটি খুদে গল্প:
মোবাইল ফোনে বন্ধুত্বের পরিণাম
অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রবিন। পড়াশোনায় ভালো হলেও ইদানীং সে একটু বদলে গেছে। কারণ তার হাতে এসেছে একটি স্মার্টফোন। সেই ফোনই তার 'নতুন বন্ধু', আর সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই সে জড়িয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত খেলায়। ফেসবুকে তার সাথে পরিচয় হলো একটি মেয়ের, যার নাম রেশমা। রেশমা দেখতে কেমন, কোথায় থাকে, কিছুই রবিন জানে না। শুধু জানে, রেশমা খুব মজার মজার কথা বলে।
প্রথমদিকে রবিন শুধু রাতে বাবা-মা ঘুমিয়ে গেলে চুপিচুপি ফোন নিয়ে রেশমার সাথে কথা বলত। এরপর কথা বলার সময় বাড়তে লাগল। রাত জেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাটিং, ভিডিও গেম খেলা—এসবই তার রুটিনে পরিণত হলো। স্কুলের পড়াশোনায় তার মন বসতো না, ক্লাসে মনোযোগ থাকত না। হোমওয়ার্ক অসম্পূর্ণ থাকত, পরীক্ষায় নম্বর কমতে শুরু করল। বাবা-মা লক্ষ্য করলেন রবিনের পরিবর্তন, কিন্তু এর কারণ বুঝতে পারলেন না।
একদিন রবিনের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো। কিন্তু সারা রাত জেগে মোবাইল চালানোর কারণে তার মাথা ব্যথা করছিল, চোখে ঘুম লেগেছিল। পরীক্ষার হলে বসেও সে কিছুই মনে করতে পারছিল না। তার সারা বছরের পরিশ্রম যেন মোবাইলের পেছনেই জলে গেল। ফলাফল বেরোলে দেখা গেল, সে সব বিষয়েই আশানুরূপ নম্বর পায়নি, এমনকি একটি বিষয়ে ফেলও করেছে।
রবিনের বাবা-মা এই ফলাফলে খুব হতাশ হলেন। তারা রবিনের ফোন চেক করে বুঝতে পারলেন আসল কারণ। রাগে-দুঃখে বাবা তার মোবাইল ফোনটি নিয়ে নিলেন। রবিন তখন বুঝতে পারল, সে কত বড় ভুল করেছে। তার 'মোবাইল বন্ধু' রেশমা তখন আর তার পাশে নেই, কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি আর বাবা-মায়ের কষ্টটা স্পষ্ট। সে উপলব্ধি করল, মোবাইলে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তা ছিল কেবল একটি রঙিন ছলনা। সত্যিকারের বন্ধু হয়তো কঠিন সময়ে পাশে থাকে, কিন্তু মোবাইল ফোন কেবল সময় আর ভবিষ্যতের ক্ষতিই করে। রবিন সেদিন সিদ্ধান্ত নিল, আর কখনো সে ফোনের পেছনে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করবে না, সত্যিকারের বন্ধুত্বের মূল্য দেবে এবং নিজের পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।
১২. (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার:
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার: এক নতুন দিগন্ত
একবিংশ শতাব্দী তথ্য ও প্রযুক্তির শতাব্দী। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি—সবকিছুতেই তথ্য ও প্রযুক্তি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার কেবল জ্ঞানকে সহজলভ্য করেনি, বরং শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয়, কার্যকর এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তুলেছে।
তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা:
তথ্যপ্রযুক্তি, বিশেষত ইন্টারনেট, শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার উন্মুক্ত করেছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা মুহূর্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। ই-বুক, অনলাইন লাইব্রেরি, জার্নাল এবং গবেষণা প্রবন্ধের সহজলভ্যতা শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বাড়িয়েছে। গুগল স্কলার, উইকিপিডিয়া, বা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে আরও গভীর করতে পারছে। এটি গতানুগতিক লাইব্রেরি নির্ভরতার পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান অর্জনের এক নতুন পথ দেখিয়েছে।
প্রযুক্তির প্রয়োগ:
শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্নভাবে শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছে:
-
ই-লার্নিং ও অনলাইন কোর্স: কোভিড-১৯ মহামারীর সময় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। জুমি, গুগল মিট, মাইক্রোসফট টিমস-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই ক্লাসে অংশ নিতে পারছে। Coursera, edX, Khan Academy-এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো বিশ্বমানের শিক্ষা কোর্স প্রদান করছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
-
স্মার্ট ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কনটেন্ট: আধুনিক স্কুল ও কলেজগুলোতে স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে ক্লাসরুমকে আরও ইন্টারেক্টিভ করা হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, ভিডিও, অ্যানিমেশন এবং সিমুলেশন ব্যবহার করে জটিল বিষয়গুলো সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।
-
গেমিফিকেশন: শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করতে গেমিফিকেশন পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ছে। শিক্ষামূলক গেম ও অ্যাপস শিক্ষার্থীদের খেলার ছলে শিখতে উৎসাহিত করে।
-
শিক্ষকদের জন্য সহায়তা: প্রযুক্তি শিক্ষকদের জন্য গবেষণা, পাঠ পরিকল্পনা তৈরি, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ও টুলস শিক্ষকদের কাজকে সহজ করে তুলেছে।
-
দূরশিক্ষণ: প্রযুক্তির কল্যাণে দূরশিক্ষণ (distance learning) পদ্ধতি আরও কার্যকর হয়েছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করছে।
সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ:
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক সুবিধা রয়েছে, যেমন: শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, স্ব-শিক্ষার সুযোগ তৈরি, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়, এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। তবে এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে:
-
ডিজিটাল বিভাজন: ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা সব শিক্ষার্থীর কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না, যা ডিজিটাল বৈষম্য তৈরি করে।
-
প্রশিক্ষণের অভাব: অনেক শিক্ষক এখনো প্রযুক্তি ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ নন, তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।
-
অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা: প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।
-
সাইবার নিরাপত্তা: অনলাইন শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ডেটা নিরাপত্তা এবং সাইবার বুলিং এর মতো ঝুঁকি থাকে।
উপসংহার:
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার এখন আর বিকল্প নয়, বরং অপরিহার্যতা। এটি একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতির জন্ম দিয়েছে যা আগামী প্রজন্মের জন্য আরও উন্মুক্ত, সহজলভ্য এবং কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করবে। তবে এই প্রযুক্তিকে সুষমভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।