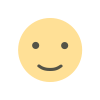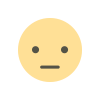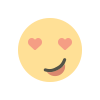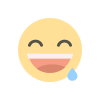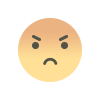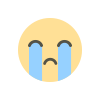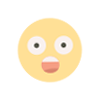এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
এইচএসসি বাংলা ২য় পত্র। ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ । CQ সমাধান
(১) 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের নিয়ম ও শব্দের উচ্চারণ
(ক) 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ:
১. আদিতে ই-কার বা ঈ-কার অথবা উ-কার বা ঊ-কার থাকলে: শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনি থাকলে এবং এরপর যদি ই-কার/ঈ-কার অথবা উ-কার/ঊ-কার থাকে, তাহলে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয়।
* উদাহরণ: অতীত (ওতিত্), অনুরোধ (ওনুরোধ)।
২. আদ্য 'অ'-এর পরে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে: শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়।
* উদাহরণ: অন্য (ওনো), অত্যাচার (ওত্তাচার্)।
৩. আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে: আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়।
* উদাহরণ: অক্ষ (ওক্খো), রক্ষা (রোক্খা)।
৪. সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের মধ্যবর্তী 'অ': বাংলা ভাষার কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের মধ্য 'অ' 'ও'-কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ: পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাশি)।
৫. শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে: শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়।
* উদাহরণ: কর্ম (কোর্মো), ধর্ম (ধোর্মো)।
(খ) শব্দের উচ্চারণ:
-
একাডেমি: উচ্চারণ সম্পর্কিত সরাসরি বাংলা উচ্চারণ পাওয়া যায়নি। ইংরেজি উচ্চারণে /əˈkæd.ə.mi/ (অ্যাকাডেমি) হিসেবে দেখা যায়।
-
গ্রীষ্মকাল: গ্রিশ্\u200cশোঁকাল
-
জিহ্বা: জিউভা
-
উহ্য: উজ্\u200cঝো
-
অনিঃশেষ: ওনিশশেশ
-
সমন্বয়: (এই শব্দের সরাসরি উচ্চারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।)
-
ব্রাহ্মণ: ব্রাম্\u200cহোন
-
উন্মাদ: (এই শব্দের সরাসরি উচ্চারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে অর্থ উন্মত্ততা, পাগলামি।)
(২) বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের নিয়ম ও শুদ্ধ বানান
(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের যে-কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ:
বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী, সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল 'ই' এবং 'উ' এবং এদের কারচিহ্ন ব্যবহৃত হবে।
১. ই/উ-কারের ব্যবহার: সকল অতৎসম শব্দে কেবল হ্রস্ব ই (ি) এবং হ্রস্ব উ (ু) ব্যবহৃত হবে।
* উদাহরণ: আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বাঙালি, বাড়ি, বুড়ি, বেশি, বোমাবাজি, মামি, মালি, মাসি, রানি, রুপালি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিন্দি, হেঁয়ালি।
২. পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি': পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই-কার হবে।
* উদাহরণ: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।
৩. সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী': সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' শব্দটি দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে।
* উদাহরণ: এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি?
৪. বিদেশি শব্দে 'ণ'-এর পরিবর্তে 'ন': বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ'-এর পরিবর্তে 'ন' ব্যবহৃত হবে।
* উদাহরণ: কর্নেল, গভর্নর।
৫. বিদেশি শব্দে 'শ', 'স', 'ষ': বিদেশি শব্দে সাধারণত 'স' ব্যবহৃত হয়, 'শ' বা 'ষ' নয়।
* উদাহরণ: পোস্ট, মাস্টার, জিনিস।
(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান:
-
লজ্জাস্কর: লজ্জাকর
-
শিরচ্ছেদ: শিরশ্ছেদ
-
বিভিষীকা: বিভীষিকা
-
জিবীকা: জীবিকা
-
সাতন্ত্র: স্বতন্ত্র
-
অধ্যাবসায়: অধ্যবসায়
-
ইতিমধ্যে: ইতোমধ্যে (ইতঃ+মধ্যে)
-
সম্বর্দ্ধনা: সংবর্ধনা
৩. (খ) নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর:
* (i) আমার **সোনার** বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
* **সোনার:** বিশেষণ
* (ii) **হে** বন্ধু, বিদায়।
* **হে:** অব্যয় (সম্বোধনসূচক অব্যয়)
* (iii) **কাকডাকা** ভোরে তার ঘুম ভেঙে গেল।
* **কাকডাকা:** বিশেষণ
* (iv) ফুল কি **ফোটেনি** শাখে?
* **ফোটেনি:** ক্রিয়া
* (v) **নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।
* **নিশীথ:** বিশেষণ
* (vi) **বিপদ** কখনও একা আসে না।
* **বিপদ:** বিশেষ্য
* (vii) **বেশ**, তাই হবে।
* **বেশ:** অব্যয় (সন্মতিসূচক অব্যয়)
* (viii) চাহিয়া দেখিলাম- **হঠাৎ** কিছু বুঝিতে পারিলাম না।
* **হঠাৎ:** ক্রিয়াবিশেষণ
উপসর্গ এবং সমাস নির্ণয়
৪. (ক) “উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই; কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।” উদাহরণসহ, উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। এই উক্তিটির অর্থ হলো, উপসর্গগুলোর নিজেদের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই যা দিয়ে তারা নিজে নিজে কোনো কিছু বোঝাতে পারে। কিন্তু যখন তারা কোনো শব্দ বা ধাতুর আগে বসে, তখন সেই মূল শব্দের অর্থে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন বা বিশেষত্ব যোগ করে নতুন অর্থ তৈরি করে। এই নতুন অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতাই হলো অর্থদ্যোতকতা।
**উদাহরণ:**
'হার' একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ, যার অর্থ 'পরাজয়' বা 'গলার হার'। এবার এর আগে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করে দেখি কীভাবে অর্থ পরিবর্তিত হয়:
* **প্র** + হার = **প্রহার** (মারধর)
* **আ** + হার = **আহার** (খাবার)
* **উপ** + হার = **উপহার** (ভেট)
* **সম** + হার = **সংহার** (ধ্বংস)
* **বি** + হার = **বিহার** (ভ্রমণ)
এখানে 'প্র', 'আ', 'উপ', 'সম', 'বি'—এই উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ ছিল না। কিন্তু 'হার' শব্দের আগে যুক্ত হয়ে তারা প্রত্যেকেই 'হার' শব্দটির অর্থে পরিবর্তন এনেছে বা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, উপসর্গের নিজস্ব অর্থ না থাকলেও, শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা বা অর্থদ্যোতকতা আছে।
৪. (খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:
* **দেশান্তর:** অন্য দেশ (নিত্য সমাস) * **কুসুমকোমল:** কুসুমের ন্যায় কোমল (উপমান কর্মধারয় সমাস) * **বিষাদসিন্ধু:** বিষাদ রূপ সিন্ধু (রূপক কর্মধারয় সমাস) * **যথারীতি:** রীতিকে অতিক্রম না করে (অব্যয়ীভাব সমাস) * **দুধেভাতে:** দুধে ও ভাতে (দ্বন্দ্ব সমাস) * **সলিলসমাধি:** সলিলে সমাধি (৭মী তৎপুরুষ সমাস) * **আশীবিষ:** আশীতে (দাঁতে) বিষ যার (বহুব্রীহি সমাস) * **সপ্তাহ:** সপ্ত অহের সমাহার (দ্বিগু সমাস)
বাক্য এবং তার বৈশিষ্ট্য
৫. (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ।
বাক্য: এক বা একাধিক পদের সমষ্টি যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা যখন কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে।
উদাহরণ:
-
ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে।
-
আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই।
একটি সার্থক বাক্যের প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক:
১. আকাঙ্ক্ষা (Expectation): বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা জাগে, তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যদি বাক্যটি শুনে মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ না পায় বা অসম্পূর্ণ মনে হয়, তবে তা সার্থক বাক্য নয়।
* অসার্থক বাক্য: আমি বই... (এখানে শোনার আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, কী করছে, পড়ছি নাকি লিখছি)।
* সার্থক বাক্য: আমি বই পড়ছি। (আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়েছে)।
২. আসত্তি বা নৈকট্য (Proximity/Contiguity): বাক্যের পদগুলো অর্থবোধক ও সুবিন্যস্তভাবে পরপর সাজানো থাকা উচিত, যাতে তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি বা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। পদগুলোর সুশৃঙ্খল বিন্যাসই আসত্তি।
* অসার্থক বাক্য: বাবা বাজার থেকে আনা ইলিশ গতকাল এসেছেন। (পদবিন্যাস সঠিক নয়)।
* সার্থক বাক্য: বাবা গতকাল বাজার থেকে ইলিশ এনেছেন। (পদবিন্যাস সঠিক)।
৩. যোগ্যতা (Competence): বাক্যের পদগুলোর মধ্যে অর্থগত এবং ভাবগত মিল বা সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, বাক্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো বাস্তবসম্মত এবং ভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
* অসার্থক বাক্য: আমরা হাত দিয়ে ভাত খাই। (হাত দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না, তাই যোগ্যতা নেই)।
* সার্থক বাক্য: আমরা মুখ দিয়ে ভাত খাই। (বাস্তবসম্মত ও যোগ্যতাসম্পন্ন)।
বাক্য রূপান্তর
৫. (খ) বাক্য রূপান্তর কর (যে-কোনো পাঁচটি):
(i) সদা সত্য কথা বলা উচিৎ। (অনুজ্ঞা)
* সদা সত্য কথা বলো।
(ii) আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)
* কী সুন্দরভাবে আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে!
(iii) আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)
* যা আমার পথ দেখাবে, তাই আমার সত্য। (অথবা, আমার পথ সেটিই দেখাবে, যা আমার সত্য।)
(iv) যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী। (সরল)
* জ্ঞানী ব্যক্তিই সত্যিকার ধনী।
(v) সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)
* সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ?
(vi) অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)
* অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।
(vii) এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক)
* এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।
(viii) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (জটিল)
* যেহেতু সত্য কথা বলিনি, সেহেতু বিপদে পড়েছি।
বাক্য শুদ্ধিকরণ
৬. (ক) যে-কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
(i) অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।
* শুদ্ধ রূপ: ছাত্রদের তপস্যা অধ্যয়নই। (বা, অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।)
(ii) আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।
* শুদ্ধ রূপ: আমি এ ঘটনা চাক্ষুস করেছি। (অথবা, আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।)
(iii) তাঁর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
* শুদ্ধ রূপ: তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
(iv) গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।
* শুদ্ধ রূপ: গীতাঞ্জলি একটি কাব্যগ্রন্থ।
(v) শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
* শুদ্ধ রূপ: শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
(vi) সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
* শুদ্ধ রূপ: সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল। (অথবা, ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।)
(vii) সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
* শুদ্ধ রূপ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। (সম্মানার্থে 'সে' এর বদলে 'তিনি' হবে)
(viii) সে আমার অধীনস্থ।
* শুদ্ধ রূপ: সে আমার অধীন।
৬. (খ) অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখ:
আসল অনুচ্ছেদ: মেয়েটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে। যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
শুদ্ধ অনুচ্ছেদ: মেয়েটি খুবই মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে। যা এর আগে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
(৭) পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ
(ক) যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:
-
Bio-data: জীবন-বৃত্তান্ত
-
Dynamic: গতিশীল
-
Adviser: উপদেষ্টা
-
Constitution: সংবিধান
-
Equation: সমীকরণ
-
Famine: দুর্ভিক্ষ
-
Hygiene: স্বাস্থ্যবিধি
-
Irrigation: সেচ
-
Legend: কিংবদন্তি
-
Memorandum: স্মারকলিপি
-
Option: বিকল্প
-
Reform: সংস্কার
-
Subsidy: ভর্তুকি
-
Tradition: ঐতিহ্য
-
Viva-voce: মৌখিক পরীক্ষা
(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
ইংরেজি অনুচ্ছেদ: Education is the backbone of a nation. No progress can be possible without education. Ignorance is like darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.
বাংলা অনুবাদ: শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের মতো। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো অপরিহার্য। এই সত্য সবার উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জাতি আশার আলো দেখতে পাবে না।
(৮) দিনলিপি রচনা / প্রতিবেদন তৈরি
(ক) তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের স্মৃতি নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।
দিনলিপি
তারিখ: ২৫শে মে, ২০২৪
সময়: বিকাল ৪:৩০
স্থান: নিজ কক্ষ
আজ আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। আজ ছিল আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন। সকাল থেকেই বুকের ভেতর এক অদ্ভুত দুরুদুরু ভাব কাজ করছিল। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই মনে হচ্ছিল যেন সময় কাটছিল না। টিভি, সংবাদপত্র – সবখানেই ফল প্রকাশের খবর। বাবা-মা দুজনেই আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের চোখেও ছিল চাপা উদ্বেগ।
বেলা বাড়ার সাথে সাথে উত্তেজনা বাড়তে থাকল। বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট বা শিক্ষা বোর্ডের সাইটে ঢোকার চেষ্টা করছিলাম বারবার, কিন্তু সার্ভার ব্যস্ত থাকায় ঢুকতে পারছিলাম না। বন্ধুদের ফোন আসছিল একের পর এক, সবারই একই অবস্থা। অবশেষে দুপুর ২টোর দিকে যখন আমি প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছি, তখন বাবা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "পেয়েছি! রেজাল্ট পেয়েছি!"
মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে। বাবার হাতে ফোন, আমি কাঁপা হাতে ফোনটা নিলাম। রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর মিলিয়ে দেখলাম – হ্যাঁ, আমিই! আর যখন দেখলাম জিপিএ ৫.০০, তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আনন্দের আতিশয্যে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল। মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বাবার চোখেও দেখলাম আনন্দাশ্রু। প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন, মিষ্টি নিয়ে আসা হলো। সারা বাড়িটায় যেন উৎসবের আমেজ।
মনে পড়ছিল বিগত দিনের কঠোর পরিশ্রম, রাত জাগা পড়াশোনা আর পরীক্ষার হলের টেনশনের কথা। আজ সবকিছুর ফল পেলাম। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুখগুলো ভেসে উঠল, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আজ আমি সত্যিই গর্বিত, আনন্দিত। এই দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতের পথচলায় এই সাফল্য আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।
(৯) চিঠি লিখন / আবেদনপত্র লিখন
(ক) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।
বিষয়: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা প্রসঙ্গে।
প্রিয় অঙ্কন,
আশা করি ভালো আছিস এবং পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস। অনেকদিন তোর সাথে সরাসরি কথা হয় না, তাই ভাবলাম তোকে একটি ইমেইল করি।
আজকে তোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য লিখছি, যা তোর জন্য খুবই জরুরি। জানি, তুই এখন প্রচুর পরিমাণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিস। এটা আধুনিক জীবনে খুব স্বাভাবিক হলেও, এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রথমত, তুই হয়তো খেয়াল করিস না, কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহার তোর পড়াশোনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। মনোযোগের অভাবে পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে তোর জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, একটানা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে, যার ফলে চোখের নানা রকম সমস্যা হতে পারে। ঘুমানোর সময়ও যদি তুই ফোন ব্যবহার করিস, তাহলে ঘুমের ব্যাঘাত হবে এবং শরীর খারাপ লাগতে পারে।
এছাড়াও, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটালে ধীরে ধীরে মানসিক সমস্যাও তৈরি হতে পারে, যেমন – হতাশা, উদ্বেগ বা আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনলাইনে নিজেকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতাও বাড়ে, যা মোটেও ভালো নয়। মনে রাখবি, বাস্তব জীবন এবং বন্ধুত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি। সরাসরি মানুষের সাথে মেশা এবং খেলাধুলা করা শরীর ও মনের জন্য খুবই উপকারী।
আমি জানি তুই বুদ্ধিমান, তাই আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছিস। আমি চাই না তোর কোনো ক্ষতি হোক। তাই অনুরোধ করব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সংযত হতে চেষ্টা করিস। পড়াশোনা, খেলাধুলা আর পরিবারের সাথে সময় কাটানোর দিকে বেশি মনোযোগ দিস।
ভালো থাকিস। আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখিস।
ইতি,
তোর দাদা/দিদি (তোমার নাম)
[তোমার ইমেইল ঠিকানা]
[তারিখ]
(১০) সারাংশ / ভাব-সম্প্রসারণ
(ক) সারাংশ লেখ:
আসল অনুচ্ছেদ: বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।
সারাংশ:
জীবনকে সার্থক করতে হলে বৃক্ষের মতো হতে হয়। শুধু নিজের উন্নতিতেই জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয় না। বৃক্ষ যেমন মাটি থেকে রস শোষণ করে ফুল ও ফল ফলায়, তেমনি মানুষকেও আত্মোন্নতির পাশাপাশি অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। তবেই জীবন সজীব ও সার্থক হয়। বৃক্ষ সার্থক জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
(১১) সংলাপ / খুদে গল্প
(ক) নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
বিষয়: নারীশিক্ষার গুরুত্ব
চরিত্র:
-
বাবা: জনাব করিম সাহেব
-
মেয়ে: রিনা, দশম শ্রেণির ছাত্রী
(সংলাপ শুরু)
রিনা: বাবা, আজ স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছিল। আমাদের বিষয় ছিল 'নারীশিক্ষার গুরুত্ব'।
বাবা: তাই নাকি? খুব ভালো খবর! তোরা কী বললি?
রিনা: আমি নারীশিক্ষার পক্ষে ছিলাম। যুক্তি দিচ্ছিলাম যে, মেয়েরা শিক্ষিত হলে শুধু নিজেরা নয়, পরিবার ও সমাজও উপকৃত হয়।
বাবা: একদম ঠিক বলেছিস মা। একটা শিক্ষিত মেয়ে মানে একটা শিক্ষিত পরিবার। সে তার সন্তানদের সঠিকভাবে মানুষ করতে পারে, পরিবারের স্বাস্থ্য ও আর্থিক বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
রিনা: হ্যাঁ বাবা। আর মেয়েরা শিক্ষিত হলে সমাজে কুসংস্কার কমে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা – এগুলোর বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে পারে। তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে।
বাবা: শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিকভাবেও মেয়েরা স্বাবলম্বী হতে পারে। একজন শিক্ষিত নারী যদি চাকরি বা ব্যবসা করে, তাহলে সে পরিবারের হাল ধরতে পারে। দেশের অর্থনীতিতেও তার অবদান থাকে।
রিনা: আমার মনে হয়, নারী-পুরুষ সমানভাবে শিক্ষিত হলেই একটা দেশ সত্যিকারের উন্নত হতে পারে। শুধু পুরুষদের শিক্ষিত করে তো আর দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রাখা যায় না।
বাবা: অবশ্যই নয়। শিক্ষা সবার মৌলিক অধিকার। একজন মেয়ে যখন শিক্ষিত হয়, তখন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। সমাজের প্রতিটি স্তরে তার অংশগ্রহণ বাড়ে।
রিনা: আমার শিক্ষিকাও বলছিলেন যে, নারীশিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি পুরোপুরি বিকশিত হতে পারে না। শিক্ষার আলো সব বাড়িতে পৌঁছানো দরকার।
বাবা: একদম সঠিক কথা। তুই খুব ভালো বলেছিস। নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সবসময় চেষ্টা করব তোকে সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে।
রিনা: ধন্যবাদ বাবা। তোমার সমর্থন পেয়ে আমি আরও অনুপ্রাণিত হচ্ছি।
(সংলাপ শেষ)
(১২) প্রবন্ধ রচনা
(গ) জাতীয় জীবনে অমর একুশের তাৎপর্য
জাতীয় জীবনে অমর একুশের তাৎপর্য
ভূমিকা: পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে যাদের মাতৃভাষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি, রক্ত দিতে হয়নি। কিন্তু বাঙালি জাতি পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা নিজেদের ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই আত্মত্যাগ বাঙালির ইতিহাসে অমর একুশ হিসেবে চিহ্নিত। এটি কেবল একটি ভাষা আন্দোলনের দিন নয়, বরং জাতীয় জীবনে এক বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা বাঙালির জাতিসত্তা বিনির্মাণে এবং স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভৌগোলিকভাবে দুই অঞ্চলের মধ্যে হাজার মাইলের দূরত্ব থাকলেও বাঙালিরা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়, যার চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেকে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করেন।
জাতীয় জীবনে একুশের তাৎপর্য:
-
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বদলে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এটি ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রথম ধাপ, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে।
-
গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ: ভাষা আন্দোলন ছিল স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধরনের প্রতিবাদ। এটি বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রথম সিঁড়ি। একুশের চেতনা থেকেই বাঙালি অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছে।
-
স্বাধীনতার বীজ বপন: ভাষা আন্দোলনই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ধাপ। এই আন্দোলন থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেমই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। একুশের পথ ধরেই বাঙালির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হয়।
-
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা: ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার অধিকার আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা রক্ষার আন্দোলনও ছিল। একুশ শিখিয়েছে কীভাবে নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হয়।
-
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: অমর একুশের আত্মত্যাগ আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাঙালি জাতির জন্য এক বিশাল গর্বের বিষয়। এর মাধ্যমে বাঙালি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য আন্তর্জাতিক পরিসরেও ছড়িয়ে পড়েছে।
-
প্রেরণা ও আত্মত্যাগের প্রতীক: একুশ বাঙালির কাছে চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এটি আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। এটি মনে করিয়ে দেয়, ভাষার জন্য, সংস্কৃতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করাও সম্ভব।
উপসংহার: অমর একুশে কেবল একটি তারিখ নয়, এটি বাঙালির জাতীয় চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। একুশের চেতনাকে বুকে ধারণ করে আমরা ভবিষ্যতেও সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকব এবং একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কাজ করে যাব—এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।